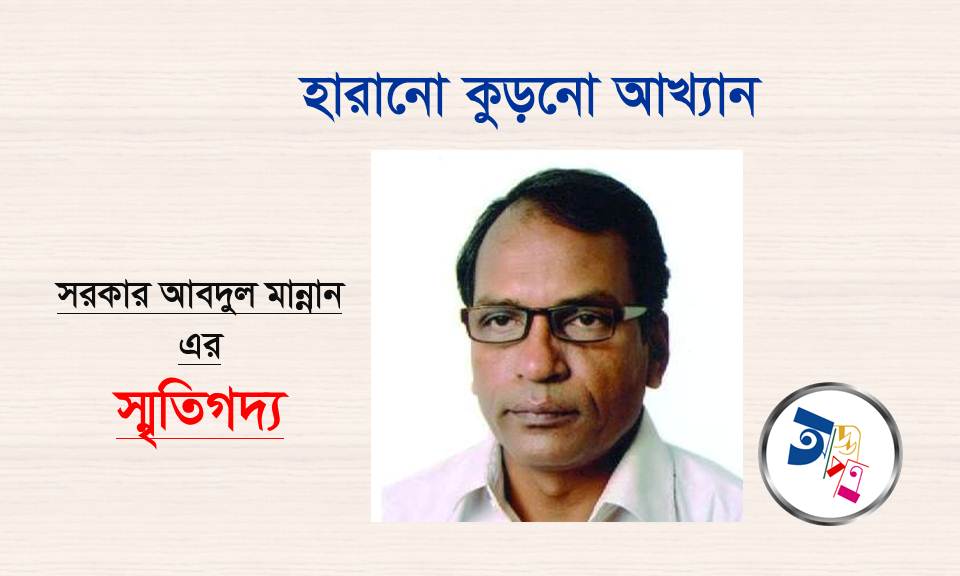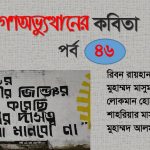সরকার আবদুল মান্নান
কত স্মৃতির ভিতর ধুলোর আস্তর জমে। একটু ফুঁ দিলে ভেসে ওঠে স্মৃতির পর্দায়। শার্সি টেনে দেখা যায় ঝলমলে রোদের ভিতর হাসছে আনন্দ-বেদনার রোদবৃষ্টি। দুঃখ-কষ্টের জমানো ব্যথা। বেড়ে উঠবার টানটান ঘটনা। আবার মিষ্টি ফুলের সুবাসও আসে জানালার ফাঁক গলে। ড. সরকার আবদুল মান্নান নিজের জীবনের সেইসব গল্পই ধুলোর চাদর সরিয়ে পাঠকের সামনে হাজির করছেন। নিজের জীবনের সাথেও তো মিলে যায় কত কিছু!
বর্ষা, ভালোবাসার ঋতু
বর্ষা। ভালোবাসার ঋতু, প্রেমের ঋতু, আসঙ্গলিপ্সার ঋতু, নিঃসঙ্গতাবোধের ঋতু এবং আরও কত কী। বর্ষা নিয়ে এমনই এক রোম্যান্টিকতার জগৎ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের শিল্পসাহত্যে। এবং সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি বর্ষা নিয়ে কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল বেদনার পটভূমিও তৈরি হয়েছে এমনই এক আবহে। কবিতায়, গানে, গল্প-উপন্যাসে, চিঠি-পত্রে, সিনেমা-নাটকে এবং এমনকি চিত্রশিল্পে বর্ষা এসেছে বিচিত্র রূপে, বিচিত্র রসে। কিন্তু তা আদিরস- কখনোই করুণরস নয়।
কালিদাসের নাম আমরা অনেকেই জানি। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা হলেও আমাদের কাছে কালিদাস মানে মেঘদূত এবং মেঘদূত মানে কালিদাস। প্রাচীন যুগের সংস্কৃত ভাষার এই কবি তাঁর মেঘদূতম কাব্যে মেঘকে কেন্দ্র করে মানবহৃদয়ের চিরকালের নৈঃসঙ্গ্য ও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার তীব্র বাসনা বাঙময় করে তুলেছেন।
অলকার অধিপতি কুবেরের কর্মচারি কোনো এক যক্ষ কর্তব্যকাজে অবহেলা প্রদর্শন করেন। সুতরাং কুবেরের আদেশে এক বছরের জন্য তাকে কৈলাসের অলকাপুরীর থেকে রামগিরি পর্বতে নির্বাসন দেওয়া হয়। রামগিরি পর্বতে তিনি নিঃসঙ্গ। প্রিয়াসঙ্গবিহীন জীবনে সেই নিবিড় বর্ষার প্রথম দিনে তার মধ্যে জেগে ওঠে আসঙ্গলিপ্সা। তিনি তার নৈঃসঙ্গ্যের কথা, ভালোবাসার কথা, আসঙ্গলিপ্সার কথা জানাতে চান তার প্রেমাস্পদকে। কিন্তু প্রেমাস্পদের নিকট তিনি কাকে দূত হিসেবে পাঠাবেন! এমন পরিস্থতিতে তার মধ্যে প্রাণ ও জড় পদার্থের পার্থক্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং তিনি মেঘকে উদ্দেশ্য করে তার প্রণয়ের কথা বলেন, তার বিরহের কথা বলেন। আর মেঘের যাত্রাপথের চিরকালের সৌন্দর্যচিত্র অঙ্কন করেন। এভাবে তিনি তার ভালোবাসার সকল আয়োজনসহ মেঘকে দূত হিসেবে অলকাপুরীতে প্রেরণ করেন।
সংস্কৃত ভাষায় রচিত চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের এই কাব্যগ্রন্থটি শুধু ওই সময়ের কবিদেরই বিপুলভাবে প্রভাবিত করেনি বরং আধুনিক যুগে বর্ষার কবিতা ও বর্ষার গান নামে সাহিত্যের একটি আলাদা ধারার উদ্ভব ঘটাতে অনুপ্রাণিত করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘নববর্ষা’ নামক প্রবন্ধ লিখেছেন :
‘মেঘ দেখিলে ‘সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ’, সুখীলোকেরও আনমনা ভাব হয়, এইজন্যই। মেঘ মনুষ্যলোকের কোনো ধার ধারে না বলিয়া, মানুষকে অভ্যস্ত গণ্ডির বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গ প্রতিদিনের চিন্তা-চেষ্টা-কাজকর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে নির্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ, সংসারের সম্বন্ধ; মেঘ সংসারের এই-সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনই হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে, কবিতায়, চিঠিপত্রে, বিশেষ কর ‘ছিন্নপত্রাবলী’তে বর্ষার যে রূপ তৈরি করেছেন তা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ষার গান আমাদের বিরহের এক চিরায়ত পটভূমিতে উপস্থিত করে। তিনি তাঁর সমগ্র রচনায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মননের যে জগৎ তৈরি করে দিয়েছেন সেই জগতের সঙ্গে তাঁর এই বর্ষাভাবনার জগৎ অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :
‘মেঘ আপনার নিত্যনূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জনে, বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে; একটা বহুদূরকালের এবং বহুদূরদেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে; তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধূ তখন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞানে জানে মাত্র; সে নিয়ম যে এখনো বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না। সেই কথাই ভাবিতে ছিলুম ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী, এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব হইয়া গেছে।”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই যে জীবনবোধ এর সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের হতদরিদ্র মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে গ্রামীণ জনপদে হতদরিদ্র মানুষের মর্মন্তুদ জীবনাল্লেখ্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় কোনো পরিচয় না থাকাতে ওই জীবন অনালোকিতই রয়ে গেছে।
প্রমথ চৌধুরী বর্ষা নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। ওইসব প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই অনুসরণ করেছেন। নিঃসন্দেহেই বর্ষার এই রূপ চিরকালীন। কিন্তু শৈশবে গ্রামীণ জীবনে বর্ষার যে রূপ দেখেছি তার সঙ্গে এইসব শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীতের রূপের মিল অতি সামান্য।
দুই.
জৈষ্ঠ্যমাস থেকেই শুরু হতো নতুন জলের আগমন। নতুন জল। ঘোলা। শরীরে ঘাসের গন্ধ, মাটির গন্ধ, খড়বিচালির গন্ধ, ধুলি-বালির গন্ধ। আর সেই জলের কি ব্যস্ততা। কত খাল, বিল, পুকু, ডোবা, নালা ভরে ভরে এগুতে হয় জৈষ্ঠ্যের জলধারাকে। এবং এর মধ্যেই শুরু হয় কর্মের জগৎ থেকে কৃষক শ্রমিকদের চলে আসার পালা।
কৃষকদের এই যে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকা শুরু হলো, তারপর আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন এবং কার্তিক মাস পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ছয় মাস এই অবস্থায় বসে থাকতে হতো। সম্পূর্ণ বেকার। তবে কিছু কাজ বর্ষাতেও করতে হতো। লাইলন সুতো দিয়ে ধর্মজাল বা ঝাকিজাল বোনার কাজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে জাল বুনতে দেখেছি বাবাকে এবং চাচা-জেঠাদের।
আনোয়ার হোসেন জেঠা জাল বুনতেন আর গান গাইতেন। তিনি ছিলেন আনন্দিত জগতর মানুষ। গান, গল্প আর কিচ্ছা, এই তিনে তার জীবন বাঁধা ছিল। এর সঙ্গে ছিল হুকায় ধুমপান। দরিদ্র মানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু কি যে এক জীবন কাটিয়ে গেছেন তা ভাবা যায় না। কোনো দিন কারো সাতে-পাঁচে ছিলেন না। ঝগড়া তো দূরের কথা, কারো সঙ্গে বেহুদা একটি কথাও বলতে দেখিনি তাকে। তিনি থাকতেন তার আনন্দ নিয়ে আর সেই আনন্দের অংশীদার ছিলাম আমরাও। কেননা, রাতে তার আসর জমত বেহুলা-লক্ষিন্দর, লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদরে চিরকালীন প্রেমেরে গল্পের বয়ানে। কি যে মমতা মিশিয়ে জেঠা পুঁথিপাঠের সুরে আমাদের এইসব গল্প শুনাতেন তার কোনো তুলনা করতে পারি না।
শুধু যে আমরা শিশুরা রাজ্যের আগ্রহ নিয়ে এইসব গল্প শুনতাম তা নয়, সব বয়সের নারী-পুরুষগণ সন্ধ্যারাতের পর থেকে জেঠার দোচালা ঘরের মাটির মেজেতে কিংবা ঘরের সামনের ছোট ওঠানে পাটি বা হোগলার বিছানা বিছিয়ে বসে পড়তেন। আমরা কেউ টেরও পেলাম না যে, কি চরম দারিদ্রের মধ্যে জেঠা এক জীবন গভীর এক প্রেমের মোহের মধ্যে কাটিয়ে গেলেন। এখন বুঝি, জীবনের প্রতি কি অসধারাণ মায়া ছিল তার। ফলে দারিদ্র্য তাকে কখনোই কাবু করতে পারেনি। তার জীবনে বর্ষাও যা, গ্রীষ্মও ছিল তা-ই।
তিন.
বর্ষায় কাজের মধ্যে ছিল আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আঠাঁই জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে পাট কাটার মতো অমানবিক কষ্টকর কাজ। এক ডুবে বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড। কাউকে কাউকে এক মিনিটও থাকতে দেখেছি। এই সময়ের মধ্যে পাঁচ থেকে সাতটি এবং এমনকি দশটি পাট কেটে উঠতেন। আর বগা কাচি কোনো কিছুতে প্যাঁচিয়ে গেলে পাট না কেটেও দম নেওয়ার জন্য ওঠে পড়তে হতো। এইভাবে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলত পাট কাটার কাজ। চল্লিশ-পঞ্চাশটি পাট নিয়ে পাটের ডগা ভেঙে কায়দা করে বাঁধা হতো মোটা বা আটি। এরপর জাগ তৈরি করা হতো। আটির উপর আটি রেখে রেখে ভেলার মতো দীর্ঘ একটি স্তূপ হলো ওই জাগ। আমরা পাটের ওই জাগের উপর ওঠে এই মাথা থেকে ওই মাতা পর্যন্ত দৌড় দিতাম। এতে জাগ যে ছুটে যেতে পারে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে আটি, সে দিকে আমাদের খেয়াল থাকত না। কিন্তু যখন বাবা বা চাচারা ‘দেখছ দেখছ, কিয়ারতেছে। জাগত ভাইঙ্গালাইতেছে’ বলে আমাদের দিকে তেড়ে আসত, তখন আমরা পানিতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে চলে আসতাম।
ক্ষেত থেকে এই জাগ নিয়ে আসা হতো বাড়ির কাছেপিঠের পুকুরে, খালে, নালা ও নর্দমায়। জাগের উপর স্তূপ করে রাখা হতো কচুরিপানা। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে পাট পচলে পাট লওয়ার কাজ শুরু হতো। পাট লওয়া মানে সংসারের সবাই তো বটেই আরও কিছু হতদরিদ্র নারীপুরুষ নিয়ে পাটকাঠি থেকে পট আলাদা করার কাজ । তারপর পাট ধোয়া ও শুকানোর।
পাট ছাড়া আর কোনো ফসল বিক্রয়ের উপযোগী করার জন্য এতটা অমানবিক পরিশ্রম আছে কি না আমার জানা নেই। পাট কাটা, পাট লওয়া ও পাট ধোয়ার কাজ করতে হতো পানিতে। ঘণ্টর পর ঘণ্টা পানি আর কাদায় থাকতে হতো। জোক শরীরের রক্ত খেয়ে আপনা থেকেই ঝড়ে পড়ত। পায়ের ও হাতের আঙুলের ফাঁকে পচন ধরত। গন্ধে ওইসব মানুষের কাছে যেতে পরত না কেউ। গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নারিকেল তেল লাগিয়ে দেওয়া হতো ঘায়ে।
পাট ঠিক মতো পচল কি না সেটা নির্ধারণ করা যেমন অনেক অভিজ্ঞতা ও সংবেদনার প্রয়োজন, তেমনি পাট শুকানোর কাজটিও ছিল খুবই তাৎপর্যময় ও চরম বিরক্তিকর।
পাট শুকানোর জন্য লাইন ধরে বাঁশের আড়া তৈরি করা হতো। তার উপর কাপড়ের মতো শুকাতে দেওয়া হতো পাট। ভিজা পাটের উপর দিয়ে বৃষ্টি হলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু একটু শুকিয়ে গেলেই আর ভিজতে দেওয়া যাবে না। সারাক্ষণ বর্ষার জলসিক্ত আকাশের দিকে নজর রাখতে হবে। কেননা, বর্ষায় আয়োজন করে বৃষ্টি হয় না। যখন-তখন নেমে পড়ে। তাই সতর্ক থাকতে হবে এবং দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি দেখার সঙ্গে সঙ্গে পাট সরিয়ে আনতে হবে নিরাপদ স্থানে। আবার আকাশের মন-মর্জি বুঝে পাট শুকাতে দিতে হবে। দিগদারির শেষ থাকত না। যদি কারো গাফিলতির জন্য শুকনো পাট ভিজে যেতো, তা হলে সব দোষ বর্তাতো মা বা দাদির উপর। অর্থাৎ গৃহকর্তার স্ত্রীর উপর। চরম গালাগাল তো আছেই, কখনো কখনো মারও খেতে হতো অভাগা স্ত্রীকে। মায়ের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের কপালেও মার জোটত।
গ্রামীণ বর্ষায় পাট শুকানোর এই যুদ্ধে স্মীর হাতে মার খেতে দেখেছি অনেক স্ত্রীকে। শুধু পাট ভিজিয়ে ফেলার জন্য নয়, সামান্য বেশি শুকিয়ে ফেলাও ছিল বিপজ্জনক। কেননা, একটু বেশি শুকিয়ে ফেললে ওজন কমে যাবে। আলগা পানি দিয়ে সেই ওজন বাড়ানো যাবে না এবং শুকনো পাটে পানি দেওয়া বিপজ্জনকও বটে। পাটের আরতদাররা সহজেই ধরে ফেলতে পারবে যে ওজন বাড়ানোর জন্য পানি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পাট বেশি শুকিয়ে ফেলার জন্যও স্ত্রীকে মার খেতে দেখেছি চোখের সামনে।
চার.
পাট লওয়া থেকে শুকানো পর্যন্ত শিশুদের সময়টা ভালোই কাটত। আমরা যারা শিশু ছিলাম, আমাদের কাজ ছিল উচ্ছিষ্ট পাট সংগ্রহ করা। পাট লইতে গিয়ে, শুকাতে গিয়ে, নিতে গিয়ে, আনতে গিয়ে নানা জায়গায় দু-চার কোয়া পাট পড়ে থাকত, ঝুলে থাকত, লটকিয়ে থাকত। বিশেষ করে নানা রকম ঝোপঝাড়, বাঁশের বেড়া, কঞ্চি বা জিঙ্গুলের ডগা ইত্যকার জায়গায় বিঁধে থাকত দু-চার কোয়া পাট। আর ওগুলো সংগ্রহ করে আমরা খইল্লাইজুর (খলিল ভাই) দোকানে বিক্রি করে তালমিশ্রি, বুট, বাদাম, চিৎ মিঠাই, গজা, বাতাসা এইসব অমৃত পেয়ে যেতাম।
পাঁচ.
জৈষ্ঠ্য মাস থেকেই পায়ে হাঁটার পথগুলো আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে যেত। একসময় এমন হতো, তখন না হাঁটা যায়, না নৌকা চলে। তখন মানুষের কষ্টের সীমা থাকত না। আমরা যারা প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম সানকিভাঙ্গা স্কুলে যাওয়ার পথে আমাদের দু-তিনটি খাল পেরুতে হতো। আর যারা নাওভাঙ্গা-জয়পুর উচ্চবিদ্যালয়ে বা এখলাসপুর হাইস্কুলে পড়ত তাদের পথে কত খাল বিল এবং জলের তোড়ে ছুটে যাওয়া রাস্তা ছিল তার কোনো হিসেব ছিলনা। আমরা ছেলেরা লুঙ্গি-প্যান্ট বাঁচিয়ে ওইসব খাল পার হয়ে যেতাম। বড়রাও নাকি তাই করত। আমরা যখন বড় হয়েছি এবং হাইস্কুলে পড়তাম তখন তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু সবসময় জলের পোশাক পরে জল পার হয়ে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। ঠিকই কিছু না কিছু ভিজে যেত। শার্ট প্যান্ট লুঙ্গি ভিজলে কোনো ব্যাপার না। পরনেই শুকিয়ে যাবে। কিন্তু যদি বই বা খাতা ভিজে যেত তা হলে সর্বনাশ।
ছয়.
স্রোতের তোড়ে ভেঙে যাওয়া রাস্তা দিয়ে প্রথমে ভালোভাবেই পার হওয়া যেত। কিন্তু মানুষের পারায় পারায় এবং জলের স্রোত আস্তে আস্তে মাটি সরে গিয়ে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি করত। তখন আর পার হওয়া যেত না। খালের উপর ছিল বাঁশের সাঁকো। অধিকাংশ সময় সাঁকোর গোড়ায় কেন যে মাটি থাকত না তা আমার বোধগম্য নয়। ওই গোড়াটার মাটি সরে সরে এখানেই তৈরি হতো আর একটি খাল। ফলে সাঁকোতে উঠার জন্য দরকার হতো আর একটি সাঁকো। বর্ষাকালে এই অবস্থা ছিল প্রায় প্রতিটি গ্রামে।
এক সময় স্কুলে আর যাওয়া যেত না। বর্ষার অনেকটা সময় এভাবেই চলত স্কুল। স্কুলে যে যাওয়া যাচ্ছে না, এবং পড়াশোনা যে বন্ধ, এই নিয়ে অভিভাবকদের কোনো চিন্তা বা দুশ্চিন্তা করতে কখনোই দেখিনি। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে গেল কি গেল না, স্কুল চলল কি চলল না এইসব বিষয় নিয়ে ভাবতে দেখিনি কাউকে। আর আমরা যারা ছোট ছিলাম, অমাদের এত বিষয় নিয়ে ভাবতে হতো যে পড়ালেখা নিয়ে ভাবার মতো সময় আমাদের কখনোই হতো না।
সাত.
কোনো কোনো সময় দিনের পর দিন বৃষ্টি হতো। ঘর থেকে বের হয়ে হাটবজারে যাওয়া তো দূরের কথা প্রকৃতি ডাকে সাড়া দেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া যেত না। আর ওঠোন থেকে শুরু করে রাস্তা-ঘাট সর্বত্র জল-কাদা।
কাদার ভেতর দিয়ে হাটঁতে হাঁটতে পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে পচন ধরত। নোখে নোকচিপা রোগ হতো। চাট্টা ডালভাত রান্না করে মানুষ যে উদর যন্ত্রণা নিবারণ করবে, সেই সুযোগও থাকত না। লাকড়ি নেই কিংবা থাকলেও ভিজা। কিন্তু না খেয়ে তো মারা যাওয়া যায় না। সুতরাং সেই দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যেই আয়োজন করতে হতো খাবারের। ভিজা লাকড়ি দিয়ে রান্না করার কষ্ট দেখেছি বহুবার। প্রচুর ধুঁয়া উদগীরণের মধ্যে খিচুরি রান্না করতে গিয়ে চোখের জলে, নাকের জলে একাকার হয়ে মা যা কিছু রান্না করতেন তাই মনে হতো অমৃত। সবকিছুতে দোষ খোঁজা আর প্যানপ্যান করা শাহজাহান ভাই বলত, ‘মা, কী রানছেন, ধুয়ার গন্ধ!”
মার তখন মেজাজ ঠিক থাকত না। বলতেন, ‘ভিজজা সব লাকড়ি পোডা পোডা অইয়া গেছে। রানছি যে এই তোগ চৌদ্দ গোষ্ঠীর ভাগ্য। খাইলে খা, না খাইলে ওঠ।”
শাহজাহান ভাই উঠত না বরং সেই সবচেয়ে বেশি খেতো।
আট.
গবাদি পশুপাখির দুর্ভোগের সীমা থাকত না। গোরু-ছগলের খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে যেত। নৌকা নিয়ে গোরুর জন্য সংগ্রহ করতে হতো খাওল্যা বা কাশ, আমন ধানের পাতা, কচুরিপানা। ভাতের মারের সঙ্গে খৈল ও খড়বিচালির অভাব দেখা দিত তখন। ছাগলের জন্য সংগ্রহ করতে হতো পাহাড়ি লতা, হিজলের ডাল, আমের ডাল, মান্দারের ডাল, কাঁঠালের ডাল। লোকে বলে, ‘পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কি না খায়।’
পাগলে কী বলে না-বলে সে সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা নেই। কিন্তু ছাগলে যে সব খায় না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। বরং ছাগলের মতো নবাব প্রকৃতির গৃহপালিত প্রাণী দ্বিতীয়টি নেই। নাক দিয়ে শুঁকে শুঁকে দেখবে, খাওয়া যায় কি না। পছন্দ না হলে খাবে না। আচ্ছা! পছন্দ হয়নি, খাসনি, চুপচাপ থাক। তা থাকবে না। বে বে চিৎকার করে পাড়া মাতিয়ে তুলবে। কিন্তু গোরুরা সত্যিকার অর্থেই গোরু। বর্ষার সেই চরম দুর্দিনে ওদের যা দেবেন মুখ বুজে তাই খেয়ে নেবে। জাবর কাটবে। তালাজ্বালা করবে না। পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও মুখে গোরু গোরু ভাব নিয়ে হাবাগোবার মতো সময় কাটিয়ে দেবে। কিন্তু ছাগল! আর বলতে চাই না। এই জন্যই বলে ছাগল পালে পাগলে। আপনি পাগল হয়ে ছাগল কিনতে পারেন কিংবা ছাগল কিনে পাগল হতে পারেন। যখনই হন, পাগল আপনাকে হতেই হবে।
মোরগ-মুরগিরা তেমন সমস্যা নয়। খুদকুড়া, ধান আর ডালচাল দিয়ে ওদের ম্যানেজ করা যায়। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ওরা বের হয় এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে কিৎকিৎ কিৎকিৎ করে ঘুরে বেড়ায়। আর হাঁসদের তো পোয়াবারো। তারা যে শুধু ডাঙ্গায় ক্যাৎক্যাৎ ক্যাৎক্যাৎ করে কাদা থেকে কেচো বের করে খায় তা নয়, আঠাঁই পানিতে পশ্চাৎদেশ উপরে তুলে ডুব দিয়ে কী যে খায় সারাক্ষণ তা ওরাই ভালো বলতে পারবে।
যত কষ্ট মানুষের।
নয়.
পানি বাড়তে থাকে। একসময় বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া পথঘাট তলিয়ে যায়। কোলাকাঞ্চির শাকসবজির ক্ষেত তলিয়ে যায়। পানি আরও বাড়তে থাকে। একসময় বাড়ির উঠোনে ওঠে আসে জল। গোরুর গোয়াল পানিতে ডুবে যায়। হাঁটু সমাস পানিতে দাঁড়িয়ে থাকে গোরু । ভাটায় যদি পানি কমে, তা হলে শুতে পারবে গোরু। আপনারা হয়তো বলবেন, ওই সময় তো মানুষের অবস্থাই শোচনীয়, গোরুর কথা চিন্তা করছেন কেন? কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনে মানুষের চেয়ে গোরুর মূল্য কম ছিল না। তাই পাড়াপ্রতিবেশিদের দেখেছি, সন্তান-সন্ততি নিয়ে তারা যত না উদ্বিগ্ন থাকতেন তার চেয়ে অনেক বেশি দুশ্চিন্তায় থাকতেন গবাদি পশু নিয়ে। কেননা, গবাদি পশুর সঙ্গে উপার্জনের সম্পর্ক, সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে তখনো সেই সম্পর্ক হয়তো তৈরি হয়নি।
কখনো কখনো পানি আরও বাড়তে থাকে। তখন ঘরে থাকা দায় হয়ে ওঠে। বাড়িতে যে ঘরটা সবচেয়ে উঁচু, সবাই ওই ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গ্রামে যে জায়গাটা উঁচু সেখানে আশ্রয় নেয় বানভাসি মানুষ।
বিপুল জলরাশির মধ্যে তখন পান করার জলটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। গোসল করার উপায় থাকে না। ধোয়ামোছার কাজগুলোও কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ছোট-বড় নানা রকম নৌকা, কলাগাছের ভেলা ইত্যাদি হয়ে ওঠে একমাত্র নির্ভরস্থল।
আজকে অনেক জায়গায় আশ্রয় কেন্দ্র হয়েছে। বানভাসি মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে পারে। এমনকি গবাদি পশুপাখি নিয়েও আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারে। কিন্তু সত্তরের দশকে এমনকি আশির দশকেও এই ধরনের কোনো আশ্রয়কেন্দ্র ছিল না। বিপুল জলরাশির মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া অসহায় মানুষের দিকে তাকানোর কেউ ছিল না। কার বাড়ির কোন ভিটা একটু উঁচু সেখানে গিয়ে মানুষ আশ্রয় নিত।
দশ.
কালিদাসের মতো, রবীন্দ্রনাথের মতো, প্রমথ চৌধুরীর মতো বুদ্ধদেব বসু তাঁর তপস্বী ও তরঙ্গিণী নাটকে রাজপুরহিতের সংলাপে বলেছেন :
আদি উৎস জল। একই স্রোত অন্তরিক্ষে ভূতলে,
ঔরসে ও বৃষ্টিতে, নির্ঝরিণী ও নারীগর্ভে;
জন্ম দেয় জল, অন্ন দেয় জল, জলে জাগে প্রাণস্পন্দন ও প্রেরণা।
জল আর জীবন জন্ম-জন্মান্তরের সখা। জল নেই তো জীবন নেই। কিন্তু জীবন না থাকলে জল থাকবে কি না জানিনা। অবশ্য জীবন না থাকলে জল থাকল-কি না-থাকল, তা নিয়ে ভেবে কাজ নেই।
এই জল আমাদের জীবনে কখনো কখনো কী গভীর সঙ্কটের কারণ হতে পারে তা কিন্তু মহান কবিগণ কখনোই ভাবেননি। কেউ যদি ভেবেও থাকেন সেই ভাবনানিচয়ের ফসল মহৎ কবিতার মহিরূহ রূপ ধারণ করে আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়নি।
কিন্তু বর্ষার এই জল দায়িত্বশীলদের জন্য কল্পনাতীত কষ্টের কারণ হলেও তার আরেকটি পিঠ আছে, যার রূপ-রস ভিন্ন। আর সেই পিঠে বিচরণ কতো শিশু-কিশোররা। যখন আমাদের জীবনে কোনো কিছুর অভাব থাকে না, তখনই আমরা খুব অভাববোধ করি।
এখন এই নাগরিক জীবনে অভাবের শেষ নেই। টুথব্রাসের অভাব, টুথপেস্টের অভাব, টিসু পেপারে অভাব, সাবানের অভাব, সেম্পুর অভাব।
কেননা এগুলো সবসময় ঘরে থাকে। একদিন যদি কোনো কারণে না থাকে তখন যে অভাব বোধ করা হয়, তার কোনো তুলনা চলে না।
শৈশবে আমাদের মধ্যে অভাবের কোনো বোধ তৈরি হয়নি। প্রকৃতির মতোই এক চিরন্তন পূর্ণতার মধ্যে আমরা বসবাস করতাম। মাকে কখনো ‘নাই’ বলতে শুনিনি। ‘নাই’ কী করে হয়! সবই তো আছে। আর এই ‘আছে’-র বোধ সবচেয়ে প্রবল থাকত শিশুদের মধ্যে। আমাদের কলা গাছ আছে, বাঁশের কঞ্চি আছে, রশি আছে। সুতরাং ভেলা বানাতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং আমরা কলাগাছের ভেলা বানাতাম, কলার ঠোঙা দিয়ে নৌকা বানাতাম, জাহাজ বানাতাম। এবং এইসব নিয়ে জলের মধ্যে কেটে যেত আমাদের দিনমান।
এখন মনে হয়, বর্ষার ওই যে দুর্বিসহ জীবন, তা কি সত্যি দুর্বিসহ ছিল? দ্বন্দ্বে পড়ে যাই। কই, কাউকেই তো হাহুতাশ করতে দেখিনি কখনো। তা হলে কি ওই জীবনও ছিল প্রকৃতির মতোই পূর্ণতর, সহজ-সুন্দর! এবং তার জন্যই কবিতায় গানে পূর্ণতার চিত্র আর চিরকালের বিরহবোধ! জানি না।