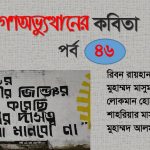সরকার আবদুল মান্নান
কত স্মৃতির ভিতর ধুলোর আস্তর জমে। একটু ফুঁ দিলে ভেসে ওঠে স্মৃতির পর্দায়। শার্সি টেনে দেখা যায় ঝলমলে রোদের ভিতর হাসছে আনন্দ-বেদনার রোদবৃষ্টি। দুঃখ-কষ্টের জমানো ব্যথা। বেড়ে উঠবার টানটান ঘটনা। আবার মিষ্টি ফুলের সুবাসও আসে জানালার ফাঁক গলে। ড. সরকার আবদুল মান্নান নিজের জীবনের সেইসব গল্পই ধুলোর চাদর সরিয়ে পাঠকের সামনে হাজির করছেন। নিজের জীবনের সাথেও তো মিলে যায় কত কিছু!
প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে : ২
শাহজাহান ভাই আর আমি পিঠাপিঠি ছিলাম না। আমার বড় তাহমিদা, তারও বড় শাহজাহান। কিন্তু মজার বিষয় হলো, তাহমিদাকে ডিঙিয়ে আমার সঙ্গে পিঠাপিঠির মতো হয়ে যায় শাহজাহান ভাই। ছোটবলায় ওর টাইফয়েড হয়েছিল। ফলে ওর বৃদ্ধি গিয়েছিল থেমে। ছোট হয়েও এক সময় আমি ওর সমান হয়ে যাই এবং ক্রমে ক্রমে ওর চেয়ে লম্বা। সব কিছু মিলিয়ে ওর সঙ্গে আমার বেশ মানিয়ে যায়। দিনের অধিকাংশ সময় শাহজাহান ভাই আর আমি একসঙ্গে থাকতাম, তা কিন্তু নয়। ওর একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল। তাদের সঙ্গে ও থাকত। আমার ফ্রেন্ডদের সঙ্গে আমি থাকতাম। কিন্তু মুশকিল হলো, শাহজাহান ভাই যে আমার অনেক বড় এটা সে ভুলতে পারত না। দেখা হলেই আমার উপর মাতব্বরি ফলাত। আদেশ নির্দেশ উপদেশ দিত। আর আমার কখনোই মনে হতো না যে, শাহজাহান ভাই আমার বড়। ফলে ওর মাতব্বরিকে আমি একদম পাত্তা দিতাম না। ও যদি আমাকে একটা বলত, আমি বলতাম দশটা। ফলে ওর আমার সম্পর্কটা হয়ে ওঠে নিরন্তর ঝগড়ার। খেলতে গেলে ঝগড়া, মাছ ধরতে গেলে ঝগড়া, গোসল করতে গেলে ঝগড়া। আর খেতে বসলে মহা ঝগড়া।
এইসব ঝগড়ায় মার কিন্তু খেতো শাহজাহান ভাই-ই। বিশেষ করে মা-র হাতে। আমি আস্তে করে এমন একটা কথা ওকে বলতাম ও যেন তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। ও তাই করত আর মা-র হাতের মুখ্খি আর চড়চাপর খেতো। মা ওকে মারত আর ও মার খেতো আর ঝগড়া করত – ‘এহ্, আমারে হস পাইছে। হের পুতেরে কিছু কয় না। হের পুতে ধোয়া তুলসী পাতা। কাইল্লাডা শয়তানের শয়তান।’ ইত্যাদি। কিন্তু দৌড় দিত না। এমন পরিস্থিতি হলে আমি এক দৌড়ে কোথায় চলে যাব তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। মা, বাবা এমনকি রুহুল আমিন ভাইও আমাকে খুঁজে পেত না। এবং আর পেটে ক্ষুধা না লাগলে বাড়ি আসার নামটি থাকত না। আর শাহজাহান ঘুরে ঘুরে মা-র কাছেই থাকবে, মা-র সঙ্গে হাজারটা জেরা করবে আর মার খাবে।
শাহজাহান ভাইকে কোনো কাজের কথা বললে তার প্রথম জবাব হলো, ‘পারতাম না। আমনের পুতেরে কইতে পারেন না?”
তার পরই হয় বকা না হয় চড়চাপর। কিন্তু কাজটা শেষপর্যন্ত ওই করবে। মাঝে কিছু ঝামেলা করতেই হবে। মা বলেন, ‘ওর খাইচ্ছত”। শাহজাহান ভাইয়ের এই স্বভাব কখনোই ত্যাগ করতে পারেনি। আর আমাকে যদি মা কিংবা বাবা কোনো কাজের হুকুম দিতেন তা হলে বলতাম, মা, যাইতাছি, করতাছি ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক সময় আমি কিন্তু কাজটা করতাম না। ওই কজটিও শাহজাহান ভাইকেই করতে হয়তো।
একসময় গোরু দিয়ে ধান মড়াই দেওয়া হতো। মড়াই শেষে খড়গুলো রেখে আসতে হতো বাড়ির বাইরে। শাহজাহান ভায়ের পীড়াপিড়িতে বাবা একটি বোঝা তুলে দেন আমার মাথায়। কিন্তু মাথা ঘুরতে ঘুরতে বোঝাটি ওখানেই পড়ে যায়। বাবা বুঝতে পেরেছেন এই ছেলেকে দিয়ে কায়িক পরিশ্রম সম্ভব নয়। ওই ঘটনার পর আমাকে আর কখনই মাথায় বোঝা নিতে হয়নি। শাহজাহান ভাই বাবাকে বলে, ‘এইডা অইল আমনের ছেলের বক্কুছক্কু। শয়তানের হাড্ডি। ভং করছে।’ বাবা বলেন, ‘ভং করলে করছে। তোর যদি ইচ্ছা না হয় তুইও চইলা যা। কাজ পড়ইয়া থাকব না।”
বাবা কাজ করবেন আর শাহজাহান ভাই চলে যাবে এমনটা কখই হতে পারে না। ভাই সব কাজই শেষ করে গোসল করতে যায়। এক সময় আমারে ডাকে, ‘এই মন্নান হুন। সত্যি কতা ক তো, তোর কি মাতা গুরাইছে?’ আমি বললাম, ‘ভাই বিশ্বাস করেন, আমি অনেক চেষ্টা করছি বোঝাটা মাথায় রাখতে। পারি নাই। মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বোঝাডা পইরা গেল।’ ভাই বলল, ‘বাদ দে। তোর আর মাথায় বোঝা নেওয়ার দরকার নাই। ঠিক মতো পড়িস। বোঝা যা নেওয়ার আমিই নিমু।’
ঘরের ভেতরে ছিল বাঁশ আর কাঠের তৈরি দুই হাত উঁচু একটা মাচার। ওটাকে বলা হতো উগুর। ওর উপর রাখা ছিল মাটির তৈরি ছোটবড় অনেকগুলো মটকা, কলস বা ঠিল্লা। বিশাল মটকাটির মধ্যে রাখা হতো ধান। কোনোটার মধ্যে চাল, কোনোটার মধ্যে গম। এভাবে মটর, কাউন, তিল, সরিষা, তিসি, গর্জন, ভেরেন্ডা, শুকনা মরিচ, মাসকলাই, খেসারী, মসুর, মুগ, হলুদ, ধনিয়া এইসব রাখার জন্য আলাদা আলাদা মাটির কলস বা বাঁশের ও বেতের পাত্র ছিল। এ যেন বিশাল একটা চিড়িয়াখানা। কিন্তু মুশকিল হলো, কোনটার মধ্যে কী আছে তা লেখা থাকত না। মা চোখ বন্ধ করে বলতে পারতেন কোন পাত্রে কী রাখা আছে। মা শাহজাহানকে যদি বলতেন, ‘শাজাহান, উগুরথিকা মুসুরির ডাইল আন।’ শাহজাহান ভাই কিছুতেই ওই পাত্রটি খুঁজে বের করতে পারত না। তখনই ঝগড়া শুরুকরে দিত। বিষয় হলো আমাকে না বলে তাকে কেন বলা হলো।
সেই সময় পাটের তৈরি সিকার মধ্যে নানা জাতের কাচের বোতল ও মাটির পাত্র ঝুলিয়ে রাখা হতো। এইসব বোতল বা মাটির পাত্র কোনোটাই খালি থাকত না। কেরোসিন তেল, সরিষার তেল, তিলের তেল, তিসির তেল, ভাজা মরিচ, পিপড়া থেকে রক্ষা করার জন্য রান্না করা খাবারও এইসব সিকায় ঝলিয়ে রাখা হতো। এ ছাড়া আরও কত কী যে পাটের সিকায় ঝুলিয়ে রাখা হতো তার ইয়ত্তা নেই। মা যদি শাহজাহান ভাইকে বলতেন সরিষার তেলের বোতলটা নিয় আয়। শাহজাহান ভাই নিয়ে যেতো কেরোসিন তেলের বোতল। মা তখন দুএক ঘা লাগিয়ে শাহজাহান ভাইকে তাড়িয়ে দিতেন। আর ওই ঝাল এসে মিটাত আমার উপর, ‘এই নবাব, তুই কই আছিলি? সারাক্ষণ ঘুইরা বেড়ানো! আইজকা যাইস খাইতে। মায় দেখাইব অনে মজা।’
খেতে বসলে ওর আবদারের শেষ থাকত না। ওটা খাবে। ওটা খাবে না। বড় মাছটা কে খেল? দুধের শর কে খেয়েছে ইত্যাদি। আর আমার পাতে কী দিল সেই দিকে ছিল শাহজাহান ভাইয়ের সতর্ক দৃষ্টি। মাকে বলত, ‘হের ছোড পুতেরেই বড়ডা দেয়। খাইতাম না আমি।’ কিংবা ‘অই তো, আমনের ছোড পুতেরেই তো সব দিয়ালাইছেন, আমি কী খামু?’
বিশেষ করে মাছ খাওয়ার ব্যাপারে শাহজাহান ভাইয়ের মারাত্মক সমস্যা ছিল। কাঁটাওয়ালা মাছ ও কখনোই খেতে পারত না। কিন্তু পাতে নিত। পাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে মাকে বলত, ‘খাইতাম না। কাডার ভরা।’ মা বলতেন, ‘কাডা ভরা তয় নিছস কিলিগা? দে, বাইছা দেই।’ মা কাঁটা বেছে দিতেন আর ও খেত। এর মধ্যে যদি ভুলেও একটি কাঁটা থাকত তাহলেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যেতো। মা-রও রীতিমতো মাথা খারাপ করে ফেলত। আর পিপড়া যদি খাবারের পাশে দিয়ে হেঁটেও যেত তাহলেই শাহজাহান ভাইয়ের মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো। পিপড়া কোথা থেকে আসল, কীভাবে আসল, কেন আসল, ওর খাবারেই কেন, মন্নানের খাবার দেখে না, এখানে খাবারটা রেখেছে কে, নিচে পানি দিয়ে রাখলে কী হতো, এইসব। সবার মাথা খারাপ করার অবস্থা হতো। ত্যক্তবিরক্ত হয়ে একসময় মা দিতেন মাইর।
কিন্তু ও কখনোই বেশি খেতো না। খাবারের পরিমাণ ছিল পরিমিত। আরেকটি স্বভাব ছিল সবাইকে দিয়ে খেতো। আমি অনেক সময় কারো কথা ভাবতাম না। একা একাই খেয়ে নিতাম। কিন্তু শাহজাহান ভাই বিশেষ করে আমাকে না দিয়ে কিছুই খেতো না। এমনকি আমি উপস্থিত নেই। ও কিন্তু ঠিকই আমার জন্য রেখে দিত। চাল ভাজা, সীম ভাজা, মটর ভাজা, নানা জাতের পিঠা, কাউনের মোয়া, কাচা আমের ভর্তা, কাচা কলার ভর্তা, বরই ভর্তা, এটো কলার থোর, চিৎমিঠাই, কাঠি লজেন্স এবং এমনকি আইসক্রিম পর্যন্ত আমার জন্য রেখে দিত।
চিংড়ি মাছ ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়। সেটা শাহজাহান ভাই জানত। ভাত খাওয়ার সময় ভাতের সঙ্গেই আমি চিংড়ি মাছগুলো খেয়ে নিতাম। আর ও প্লেটের কানায় চিংড়িগুলো সারি করে সাজিয়ে রাখত। ভাত খাওয়া শেষ হলে খাবে। মা তখনই বুঝতেন, ঝগড়ার একটা আয়োজন হচ্ছে। মা তাড়া দিতেন, ‘এই শাহজাহান, চিংড়িগুলি এক্ষণ খা। এগুলি জোলাইয়া রাখছস কিলিগা? ঝগড়া বাধানোর উস্তাদ! খা কইতাছি।”
শাহজাহান কিন্তু খাবে না। পরে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে আর আমি চাইলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে। ‘কিলিগা দিতাম? তোর গুলি তুই রাখতে পারস নাই? এখন আমার কাছ থিকা চাস কিলিগা? আমি দিতাম না।’ তখনই নেওয়ার জন্য থাপাথাপি করতাম। একসময় মা এসে দৌড়ানি দিতেন। মায়ের দৌড়ানি খেয়ে দূরে গিয়ে ও আর আমি চিংড়ি মাছ খেতাম।
সকালে হোক, দুপুরে হোক, রাত হোক, খাবারের সময় আমি খেয়ে নিতাম। কারো জন্য অপেক্ষা করতাম না। কিন্তু শাহজাহান ভাই আমাকে ছাড়া কখনই খেত না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এরশাদ ভ্যাকেশনের ফাঁদে পড়ে যখন দিনের পর দিন বাড়িতে থাকতে হতো তখন সময় মতো খাবারে সুযোগ কখনই হতো না। সেই সময়গুলোতে প্রায় প্রতিদিন শাহজাহান ভাই আমার জন্য অপেক্ষা করত আর মাকে জ্বালাতন করত। ‘কই যায়? এখনো আইয়ে না কেন? আড্ডাবাজি শিখছে। পড়াশোনা তো লাডে উঠছে।’ মা বলতেন, ‘তোর খাওয়া তুই খাইয়া নে। ওর লইগা দেরি করনের দরকার আছে?’ কিন্তু শাহজাহান ভাই শুনত না। আমার জন্য অপেক্ষা করত।
বাড়ির দক্ষিণের পুকুরের ওপারে মসজিদ চত্তর। একবার ওখানে কী নিয়ে যেন ওর সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয় । ঝগড়ার এক পর্যায়ে ওর সার্টের বুক পকেট ধরে টান দিলে পকেট ছিড়ে আমার হাতে চলে আসে। আমি ওই পকেট হাতে নিয়েই দিই দৌড়। দৌড়িয়ে আমাকে ধরতে না পেরে শাহজাহান ভাই কাঁদতে কাঁদতে মা-র কাছে গিয়ে বিচার দেয়। নতুন সার্টের পকেট ছিড়ে এসেছে, এই দোষ যেন শাহজাহানেরই। সুতরাং প্রথম দফায় ও মায়ের হাতে চড়চাপর খায়। যেন সব দোষ ওরই। আমি পকেটটা আমার হাফ পেন্টের পকেটে রেখে দিই। কিছুক্ষণ পরে শাহজাহান ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ওকে যে মা ধোলাই দিয়েছে তা সম্পূর্ণ গোপন রেখে আমাকে বলে, ‘তুই আইজকা বাইত যাইস, দেখিস মা তোরে কেমন তুরা দেয়।”
আমি খুব ভয়ে ভয়ে বাড়িতে গেলাম। আর বাড়িতে না গিয়েও উপায় ছিল না। দুপুর গড়িয়ে গেছে। ক্ষুধা লেগেছে ভীষণ। মা দেখি গোসল করে এসেছেন। আমাকে দেখে খুব একটা রাগ করলেন না। শুধু বললেন, ‘শাহ্জাহানের জামার জেব ছিড়ছস কিলিগা? কই রাখছস? জেব লইয়া বাইত আবি। নইল আইজকা তোর ঠাহুরেরে কমু।”
আমার ‘ঠাহুর’ মানে বাবা। বাবার কাছে বিচার দিবেন। ভয়াবহ ব্যাপার। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাফ পেন্টের পকেট থেকে জামার পকেট বের করে মা-র হাতে দিই। মা কিছুক্ষণের মধ্যে শাহজাহানের সার্টে পকেটটি সেলাই করে লাগিয়ে দেন। মেরুন রঙের সার্টে সেলাইয়ের সুতা ছিল সাদা। কিন্তু মা এখন পকেটটি সেলাই করে দিয়েছেন মেরুন রঙের সুতা দিয়ে। ফলে খুব ম্যচ করে গিয়েছে। একদম দেখা যায় না। মার হাতে যা পড়ত তা-ই সুন্দর হয়ে যেতো। আমি অবাক হয়ে গেলাম। বোঝার কোনো উপায় নেই যে টেনে ছেড়া পকেট হাতে সেলাই করে লাগানো হয়েছে। আমি সার্টটি নিয়ে এক দৌড়ে শাহজাহান ভাইয়ের কাছে যাই। ওর হাতে সার্টটি দিয়ে বলি, ‘মারে কইছেন আমি নাকি আমনের সার্টের পকেট ছিড়ালাইছি। কই, দেহান তো।”
শাহজাহান খুব ভালো করে দেখে। আবার দেখে। আবার দেখে। ও অবাক হয়ে যায়। তাই তো, পকেট তো আছেই। আর কোনো কথা না শুনে ও এক দৌড়ে মা-র কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং মাকে বলে, ‘মা মা, মন্নানে তো পকেট ছিড়ে নাই। জামার লগে পকেট আছে।’
মা হাসেন।
বলেন, ‘ছিড়ে নাই, ভালা অইছে। এহন খাইতে ব। খাইয়া আমারে উদ্ধার কর।”
একটা চকিতে আমরা শুইতাম, ঘুমাতাম। ওর শোয়া ছিল খুবই বিশ্রী। শোয়ার পর থেকে সারাক্ষণ গড়াড়রি করত আর কিছুক্ষণ পর পর আমার গায়ের উপর হাত-পা দিত। একবার দুইবার সরিয়ে দিতাম আমি। তারপর ত্যক্তবিরক্ত হয়ে মাকে ডাকতাম। ‘মা মা, আমনের পুতে আমার শইলের উপর পাও দেয়।’ মা এসে ঠিকঠাক মতো শুইয়ে দিয়ে যেতেন। কিন্তু এই ঠিকঠাক কতক্ষণ আর থাকে? যেই লাউ সেই কদু। এক সময় ঘুমিয়ে যেতাম। সেই ঘুমন্ত অবস্থায় মা কিংবা বাবা কখনো কখনো আমার গায়ের উপ থেকে ওর হাত-পা সরিয়ে দিয়ে যেতেন। কিন্তু সবসময় এ রকম শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করত না। শুইতে গিয়ে প্রথমে মৃদু ঢেলাধাক্কা তার পর হাতাহাতি এবং পরিশেষে চরম লাথালাথি। শীতের দিনে লেপ-কাঁথা ছিড়ে যাতা অবস্থা করে ফেলতাম। কখনো কখনো মা কিংবা বাবা এসে দুএকটি চড়থাপর দিয়ে আমাকে উঠিয়ে তাদের কাছে শুয়ে দিতেন। আমি বাবার কাছে শুইতাম বটে, কিন্তু একদমই ভালো লাগত না। সারাক্ষণ উসখুস উসখুস করাতাম। একসময় যখন বুঝতাম, মা-বাবা ঘুমিয়ে গেছেন তখন সন্তপর্ণে উঠে এসে শাহজাহান ভাইয়ের কাছে ঘুমিয়ে যেতাম।
শাহজাহান ভাই আমার চেয়ে দুই ক্লাস উপরে পরত। পড়ার টেবিল ছিল আমাদের একটাই। যে চকিতে আমরা ঘুমাতা সেই চকির সঙ্গে লাগানো ছিল আমাদের পড়ার টেবিল। চকিতে বসে পড়তে হতো। শাহজাহান ভাই জোরে জোরে পড়ত, চিৎকার করে পড়ত। ওর ওই চিৎকার করে পড়ার মধ্যে মনে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও থাকত না। আর আমি পড়তাম মনে মনে। বুঝতে চেষ্টা করতাম। আমার মনে মনে পড়া নিয়ে ওর কোনো সমস্যা হতো না। যত সমস্যা হতো আমার। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো, ওর চিৎকার করে পড়াটাকেই মা-বাবা সাপোর্ট করতেন। চিৎকার করে পড়ে শাহজাহান যে আমার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করছে না, সেটা কিন্তু তারা বিবেচনায় নিতেন না। সুতরাং এই সমস্যা হজম করা ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না। কিন্তু মুসকিল হলো অন্য জায়গায়, পড়তে গিয়ে সারাক্ষণ কথা, সারাক্ষণ গল্প, সারাক্ষণ হোহো হাহা, সারাক্ষণ ঝগড়া।
খড়িমাটি দিয়ে টেবিলটাকে দুই ভাগ করা হয়েছিল। শাহজাহান ভাই যেহেতু বড় এবং পড়েও বড় ক্লাসে সেই জন্য তার ভাগে বেশি রেখে টেবিলটা ভাগ করা হয়েছে। তার পরেও তো একজনের বই খাতা পেন্সিল অন্য জনের সীমানায় চলে যেতে পারে। এবং তাই হতো। আর পড়তে গেলে এই সব নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া লেগেই থাকত।
শাহজাহান ভাই বলত,
“তোর ছোড ক্লাসের বই। তোর বই আমার বইয়ের লগে লাগে কিলিগা?”
আমি বলতাম,“কিলিগা রাগে বইয়েরে জিগান।’
শুরু হয়ে যেতো ধাক্কাধাক্কি। একদিন ও আমার সমস্ত বই খাতা পেন্সিল মাটিতে ফেলে দেয়। আমার ভীষণ মন খারাপ হয়। আমি বাবাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই, আলাদা টেবিল না দিলে আমি আর পড়ব না। ওই দিনই বাবা বাঁশ-বেত দিয়ে আমাকে আলাদা একটি টেবিল বানিয়ে দেন। আমি আমার টেবিলে পড়তে লাগলাম। শাহজাহান ভাই ওর টেবিলে পড়ে। এখন আর সে চিৎকার করে পড়ে না, মনে মনে পড়ে আর একটু পরপর পড়া রেখে আমার কাছে আসে। পড়ার জন্য আমার এই নতুন টেবিলটা মোটেই ভালো নয়। বিভিন্ন জায়গায় বাঁশ উঁচু হয়ে আছে। কাগজ দিয়ে মুড়িয়েও সমান করা যাচ্ছে না। আমি পড়া রেখে চকিতে বসে থাকি। চকির ওই প্রান্তে শাহজাহান ভাই পিছন ফিরে ফিরে আমার দিকে তাকায়।
বলে, ‘আবি, আইয়াপর। ওইডা একটা টেবিল অইল, ফালতু।’
আমি বলি, ‘আমনে তো অনেক ঝামেলা করেন। আইতাম না।’
ভাই বলে, ‘আচ্ছা। আর কাইজা করতাম না। আইয়াপর।”
অনেক কষ্ট করে বানানো নতুন টেবিলটা পড়ে থাকল খালি। আমি আগের টেবিলে চলে আসলাম। মা চিৎকার চেঁচামেচি করছেন, ‘তয় তোর বাবারে দিয়া এই গাধাখাটুনিডা কিলিগা খাটালি?’ ইত্যাদি।
শাহজাহান পড়াশোনায় একদম ভালো ছিলনা। ওর পড়াশোনার আশাও ছেড়ে দিয়েছিলেন বাবা। সংসারের প্রায় সব কাজই আস্তে আস্তে শাহজাহান ভাইয়ের কাঁধে গিয়ে পড়ে। ক্ষেত-গৃহস্থীর কাজ, কালু কাকার (কলিমুল্যা সরকার) গোরু ও লাঙলজোয়াল নিয়ে ক্ষেতে যাওয়া, কাকাকে নানা কাজে সাহায্য করা, ক্ষেত নিড়ানোর জন্য বদলিদের (কৃষিশ্রমিক) সঙ্গে থাকা, নিজেও ক্ষেত নিড়ানোর কাজে অংশ গ্রহণ করা, কখনো কখনো বর্ষাকালে শ্রমিকদের সঙ্গে ডুবিয়ে ডুবিয়ে পাট কাটা ইত্যাকার অসংখ্য কাজে শাহজাহান ভাই ব্যস্ত হয়ে যায়। আর অবসর সময়ে গ্রামময় ঘুরে বেড়ানো এবং সবচেয়ে প্রিয় হলো যখন তখন গলা ছেড়ে গান গাওয়া।
তখন বড় ভাই রুহুল আমিন আমাদের এক নানাবাড়িতে থাকছে। আর মতলব ডিগ্রী কলেজ থেকে পড়া শেষ করে চাকরি খুঁজছে এবং ঘুরে বেড়াচ্ছে। বামের বাজারে নানাদের চাল-গম ভাঙানোর কল ছিল। তার সমবয়স্ক নাদির মামার সঙ্গে চাল-গম ভাঙানোতে সময় দিত এবং মামা-ভাগনে মিলে ভালোই মারিংকাটিং করত। তারা বেশ রাজহালেই সময় কটাতো। ওই মোল্লা বাড়িটি ছিল এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য ও অভিজাত। ওই বাড়ির নামেই গ্রামটির নাম ছিল মোল্লাকান্দি। আমি অসংখ্য বার ওই বাড়িতে গিয়েছি। ওই বিশাল বাড়িটিতে গিয়ে মুক্তির আনন্দ লাভ করতাম। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল নানা-নানির আদর। তারা শুনেছেন, ছাত্র হিসেবে আমি ভালো। তার জন্য আমাকেই সবচেয়ে বেশি আদর করতেন। নানি বলতেন, ‘আমার কালো মানিক।’
আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। বড় ভাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় ভাই রুহুল আমিন আমাদের পড়াত এমন নজির খুব বেশি নেই। আমি তখন খুব ছোট। গলা ছেড়ে ছড়া পড়ি। একটি ছড়া পড়তে গিয়ে আমি লজ্জায় আটকে গেলাম। ‘আপনার বাসা আগে …’ বলে আর কিছু বলি না। চুপ হয়ে যাই। বড় ভাই সম্ভবত বাইরেই ছিল। ব্যাপারটা কী? কৌতূহলী হয়ে সে ঘরে আসে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘কীরে, পুরাটা পড়স না যে?’ আমি হাসতে হাসতে ছড়াটা এগুয়ে দিই। ভাই বলে,”তুই তো অনেক পাকনা অইয়া গেছস। এই ‘বুনি’ মানে বুনন করি। মা কাঁতা সেলাই করে না? এইডা অইল ওই সেলাই করা। বুকুদুধু না, ফাজিল কোতাকার।’
আমাদের এলাকায় ‘স্তন”কে বলে ‘বুনি’। কিন্তু বুনি এর অর্থ বুনন করি, আমার শব্দভাণ্ডারে তখনো এই শব্দ ছিল না। আমি খুবই লজ্জা পেয়েছিলাম। এ রকম দু-একবার ভাই আমাদের পড়া ধরেছিল। বাবাই আমাদের পড়াতেন। বিশেষ করে যোগ বিয়োগ পুরণ ভাগ বাবার কাছ থেকেই শিখেছি।
শাহাজাহান ভাইয়ের পড়াশোন আর হলো না। সুতরাং সংসারে বাবাকে এবং মাকে সাহায্যে করার সব দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হলো। ও সংসারের কাজ করে আর গলা ছেড়ে গান গায়। মা বলতেন, ‘ওই, শোনা শোন। শাহজাহানের গলা না। অর গানের গলাডা খুব ভালা।’ কোথায় থেকে মাইকে ভেসে আসছে গান। মা ঠিকই বুঝতে পারতেন এটা তার ছেলের কণ্ঠ। আমার বোনেরাও ওর কণ্ঠ চিনতে পারত। শাহজাহান ছিল ওদের কাছে আরেকটা বোনের মতই ভাই।
কখনো দেখিনি ভাত খেতে বসে কেউ গান গায়। শাহজাহান ভাই গাইত।
মা বলতেন, ‘অলক্ষির চারা। ভাত খাইতে বইয়া কেউ গান গায়?’
কে শোনে কার কথা। মাঝেমধ্যেই তার গলায় গান চলে আসত। আর ভাত-তরকারি দিতে গিয়ে মা-র হাতে যা থাকত তাই দিয়ে শাহজাহান ভাইয়ের হাতে বাড়ি দিতেন আর টান দিয়ে সরিয়ে নিতেন মাটির প্লেটটা। এই প্লেটের নাম সানকি বা হানক।
মা বলতেন, ‘ওঠ ওঠ, তোর খাওয়ার দরকার নাই। যা, পাড়ায় পাড়ায় গিয়া গান গা।”
শাহাজাহানরে দাঁত ব্যথা হতো। খুব কষ্ট পেতে দেখেছি ওকে। দাঁতের ব্যথায় কপালের শিরদারগুলো ফুলে যেত। কখনো কখনো হাত দিয়ে মাথায় আঘাত করত। ওর দাঁতের যন্ত্রণা দেখে সবারই কষ্ট হতো। কিন্তু প্রতিকার তো নেই কিছু। দাঁতে গুল দেয়। শুনি, কিছুটা আরাম পায়। ও আড়ালে-আবডালে মাঝমধ্যে সিগারেট খেতো। একদিন শুনি, বাবাকে বলছে সিগারেট টানলে নাকি দাঁতে আরাম পায়, ব্যথাটা কমে। বাবা রোজ পনের থেকে বিশ কাপ চা খেতেন। কিন্তু কোনো দিন পান-সিগারেট স্পর্শ করেননি। আমাদের সেই বাবা ওকে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমি তো রীতিমতো তাজ্জব। ওকি তাহলে বৈধভাবে সিগারেট খাওয়ার জন্যই এটা করেছে! কিন্তু শাহাজাহান ভাই সিগারেট যে খুব বেশি খেয়েছে না নয়। অতি সামান্য। কোনো মুরব্বি কোনো দিন ওকে সিগারেট টানতে দেখেনি।
মা-বাবার কাছে শাহজাহান কোনো দিন বড় হয়নি। বড় ভাই রুহুল আমিন অনেক বড় হয়ে গেল। বড় ভাইকে মা-বাবার গা ঘেষে থাকতে দেখিনি কখনো। শুধু দেখেছি মা যখন রান্না করতেন তখন চুলার উপরে ধুয়া উঠা তপ্ত কড়াই থেকে ছো মেরে উঠিয়ে নিচ্ছে শাক, তরকারি, মাছ, মাংস। বিশেষ কর শাক রান্নার সময় চুলার উপরেই কড়াই অর্ধেক হয়ে যেতো। বড় ভাইয়ের দেখাদেখি আমরাও এই কর্মে বেশ পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলাম। তবে প্রথম প্রথম মুখে দিয়ে আবার বের করে আনতে হতো। না বুঝে বেশি গরম পুরে দিতাম। বড় ভাইকে এ সময় আমরা বেশ অন্তরঙ্গ অবস্থায় পেতাম। অসাধরণ এই সহজ-সরল মানুষটি সারাক্ষণ উচ্চস্বরে হোহো হাহা করে হাসে। জীবনের কোনো দুঃখ-কষ্টকে কোনো দিনই পাত্তা দেয়নি। আমরা যখন ঘরের মেঝেতে পিড়ি পেতে খেতে বসতাম, তখন বড় ভাই আমাদে দৃষ্টি অন্য দিকে নেওয়ার জন্য বলত, ‘ওই দেখ কালা বিলাই।’ আমরা সেদিকে তাকাতাম। আর সেই ফাঁকে আমাদের প্লেট থেকে উধাও হয়ে যেতো চিংড়ি মাছ, শাক, গোস্ত। কখনো টের পেতাম। কখনো পেতাম না। ভাত দিয়ে আড়াল করে ফেলত। বুঝতে পারলে চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরুকরতাম। বলতাম, ‘এহ্, আমারে বক্কু দিতে পারবেন না।’ এমন কিছু সময় আমরা বড় ভাই রুহুল আমিনকে সংসারে পেতাম। বাকি সময় লাপাত্ত। বাবা-মার সঙ্গে তার তখন সমভ্রমের সম্পর্ক।
আমিও অনেক বড় হয়ে গেলাম। নাইনে পড়ি। কীভাবে যেন মা-বাবার সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। লজিং থাকি এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পেছনে অবস্থিত চেয়ারম্যান মনু সিকদারের বাড়িতে। একটা বেটা বেটা ভাব নিয়ে সংসারে দূরের কেউ হয়ে গেলাম। কিন্তু শাহজাহান ছোটই থাকল। স্কুলে যায় না। সারাক্ষণ মা-র গা ঘেষে থাকে। সংসারে কাজ করে। ঝগড়া করে। বকা খায়। মার খায়। আর মা-বাবার অফুরন্ত ভালবাসা ও স্নেহের মধ্যে আনন্দে থাকে আর গান গায়।
১৯৭৮ সালে বড় ভাই রুহুল আমিন বিয়ে করেন। আগেই বলেছি, আমি নাইনে পড়ি। শাহজাহান নাওভঙ্গা-জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সিক্স বা সেভেনে পড়ে ইস্তফা দিয়েছে। নতুন বউ এসে দেখে শাহজাহান স্কুলে যায় না। ভাবি শাহজাহানকে বলল, ‘তুই যে পড়স না, কী করবি, বড় ভাই আর ছোট ভাইয়ের ব্যাগ টানবি?’ ভাবি আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকেই আমরা ভাই-বোন যারা ছোট তাদের সবাইকে ‘তুই’ বলে সম্বোধন করতে লাগল আর এমন ভাবসাব নিল যে, ভাবি হিসেবে ঠাট্টা করায় কোনো সুযোগই পেলাম না। বরং মা-খালাদের মতো আমাদের যৎকিঞ্চিৎ শাসন করতে লাগল। বাবাকে বলল, ‘বাবা, কালকে শাহজাহানকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। ও পড়বে না, এটা কেমন কথা হলো?’
নতুন বউমার কথা শুনে বাবা খুব খুশি হলেন এবং সম্ভবত পরদিনই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তবে নাওভঙ্গা-জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে নয়। ওই স্কুলে ওর সঙ্গে যারা পড়ত ওরা সবাই এসএসসি পরীক্ষা দেবে আর ও পড়বে এইটে, তা হয় না। যেখানে কেউ ওকে চিনে না সেই স্কুলে ভর্তি করতে হবে। শেষপর্যন্ত ওকে ভর্তি করা হলো আমার স্কুলে। আর আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, ‘খবরদার, আমি যে তোর বড় ভাই এ কথা কাউকে বলবি না।’
আমি স্কুলের কাছে লজিং থাকি আর ও বাড়ি থেকে স্কুলে যায়। ফলে খুব যে একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় তা নয়। তবে সবাই জেনে গেছে শাহজাহান আমার বড় ভাই।
এ সময় একটা ঘটনা ঘটল। গণিতের শিক্ষক যোগেল স্যার শাহজাহান ভাইকে এমন মার মারলেন যে ওকে রক্তাক্ত করে ফেললেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ও পড়াশোনায় ভালো না। কিন্তু খুব সহজ সরল মানুষ। খুব মানবিক। মানুষের জন্য এত দরদ নিয়ে ও জন্মেছে যে কী আর বলব। এহেন শাহজাহানের প্রতি যোগেল স্যার কেন এতটা নিষ্ঠুর হতে পারলেন তা বোধগম্য নয়। বিষয়টা এলাকায় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। সানকিভাঙা ও জহিরাবাদের শিক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষক খোরশেদ স্যারকে জানিয়ে দেয়, এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হলে ওই দুই গ্রামের শিক্ষার্থীরা এখলাসপুর স্কুল বর্জন করবে। এ দিকে এলাকার চেয়ারম্যান মনু সিকদার কাকাও বিষয়টি জেনেছেন। তার বাড়িতে আমি থাকি। আমাদের পরিবারের সবাইকে তিনি চিনেন। বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শাহজাহান ভাইকে খুব স্নেহ করতেন। মনু কাকাও খুব মন খারাপ করলেন। খোরশেদ স্যারও বাবার বন্ধু। তিনি বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন। চিরকাল অন্যদের ঝগড়াঝাটির দেনদরবার করেছেন বাবা। কিন্তু এক জীবনে কখনো কারো সঙ্গে ঝগড়া করেননি বাবা। নিজের ক্ষতি স্বীকার করে শান্তিতে থাকতে চেয়েছেন সবসময়। খুব ঠান্ডা মাথার অধিকারী খুব শান্তিকামি আমার এই ভালো মানুষ বাবা বিষয়টিকে চুপচাপ সমাধান করে ফেললেন। বিশেষ করে যোগেল স্যার যেন কিছুতেই মনোকষ্ট না পান সেদিকে বাবা সতর্কত দৃষ্টি রেখেছিলেন। কিন্তু বাবা-মা যে কষ্ট পেয়েছিলেন, তা কখনোই ভুলবার নয়। ঘটনা যখন মিটে গেছে তখন শাহজাহান ভাই নাইনে উঠেছে। এই সময় বাবা তাকে এখলাসপুর স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে নাওভঙ্গা-জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এখান থেকেই শাহজাহান ভাই ১৯৮১ সালে এসএসসি পাস করে। সম্ভবত ১৯৮৭ সালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে তার চাকরি হয়। প্রথম পোস্টিং ছিল কুমিল্লাতে। ১৯৮৮ সালে বিয়ে করে।
মানুষকে আদর-যত্ন করে, আপ্যায়ন করে শাহাজাহান ভাই খুব আনন্দ পেত। ছোট বেলা থেকেই শাহাজাহান ভাই আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত-স্বল্প পরিচিত লোকদের রাস্তা থেকে প্রায় জোর করে বাড়িতে নিয়ে আসত কিছু খেয়ে যাওয়ার জন্য। কখনো দেখা যেত অতিথির সামনে দেওয়ার মতো ঘরে কিছুই নেই। তখন মা ওকেই পাঠিয়ে দিতেন দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসার জন্য। মা কোনো রকমে মানসম্মান রক্ষা করতেন। আমি একদম ওর বিপরীদ। বাড়িতে গেলে ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব ছাড়া সেধে কারো সঙ্গে কথা বলি না। লোকজন যথাসম্ভব এড়িয়ে থাকি। আগবাড়িয়ে লোকজনের কথাবার্তায় অংশগ্রহণ করিনা। যাকে যতটুকু সম্মান করার করি। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু শাহাজাহান ভাই এরকম নয়। সে আগবাড়িয়ে কথা বলতে যাবে, আগবাড়িয়ে সাহায্যসহযোগিতা করতে যাবে, মানুষের সঙ্গে বন্ধুপনা করার জন্য সবসময় মুখিয়ে থাকে। ফলে সে যেখানে থাকে সেখানেই তার সুনামের শেষ নেই। কুমিল্লায় অনেক আত্মীয়স্বজন আছে, এলাাকার অনেক লোক কুমিল্লায় থাকে। তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয় আর তার সারাক্ষণ শাহ্জাহানের প্রশংসা করে।
কুমিল্লা থেকে রোজ রোজ বাড়িতে আসতে পারে না। মা-বাবর খোঁজখবর নিতে পারে না। সুতরাং তাকে চাঁদপুর আসতে হবে এবং একসময় বদলি হয়ে চাঁদপুর চলে আসে। এখন প্রায় প্রতিদিনই বিকেলের লঞ্চে বাড়িতে চলে আসে। আবার মা-বাবার গা ঘেষে থাকার সুযোগ পেয়ে যায়।
বেতনের টাকাটা সে পুরো বাবার হাতে দিয়ে বাবার কাছ থেকে খরচের টাকা চাইবে। মাসে হাত খরচ কত হতে পারে, সেটা রেখে বাকি টাকা সে বাবা হাতে দিতে পারে। কিন্তু তা না করে প্রায় প্রতিদিনই বাবার কাছে পাঁচটাকা দশ টাকা চাইবে। একজন বেকার ছেলে যেমন বাবা-মার কাছ থেকে টাকা চায়, শাহাজাহান ভাইও তাই করে, টাকা জন্য ঘেনঘেন।
আমার প্রতিষ্ঠা নিয়ে শাহাজাহান ভাই খুব মুগ্ধ থাকত। নানা জনের সঙ্গে যখন বিচিত্র বিষয় নিয়ে কথা বলত তার একটি অংশে আমার প্রসঙ্গ থাকবেই। আমি কাপাসিয়া কলেজ থেকে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে এবং এখান থেকে ১০% কোটায় বিসিএস করে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে রাজেন্দ্র কলেজে চাকরি, এইসব অর্জনকে শাহাজাহান ভাই খুব গৌরবের সঙ্গে বিবেচনা করত। সুতরাং এমফিল শেষ করে কেন পিএইচডি করতে দেরি হচ্ছে, এই নিয়ে তার বেশ দুশ্চিন্তা ছিল।
২০০০ সালের কথা। ইতোমধ্যে শাহাজাহান ভাইয়ের এক ছেলে ও দুই মেয়ে হয়েছে, উপল, উপম ও স্বাতি। ওদের বয়স সাত বছর পাঁচ বছর ও দুই বছর। কিন্তু শাহাজাহান ভাই সেই ছোট মানুষটিই রয়ে গেছে। মা-বাবা এখন ওকে গায়ে হাত দিয়ে মারে না কিন্তু আর সবই করে।
কোরানি ঈদ। ঈদের দিন গোরু কোরবানি দেওয়া হয়েছে। পরের দিন একটি ছাগল কোরবানি দিতে হবে। বাবা শাহাজাহান ভাইকে বললেন, একজন কসাই খুঁজে নিয়ে আসতে। শাহাজাহান ভাই বলে যে, এই ছাগলটা জবাই করতে নাকি দেড়শ-দুশ টাকা চাইবে। সুতরাং দরকার নেই। আমি সহযোগিতা করলে সে-ই নাকি কোরবানি দিয়ে দিতে পারবে। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। প্রায় যুদ্ধ করে জবাই দেওয়ার কাজটা শেষ করলাম। কিন্তু চামড়া খসাতে গিয়ে পড়লাম মহা ঝামেলায়। এর মধ্যেই চামড়া কেটেকুটে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই খসাতে পারা যাচ্ছেনা। দুই জনের মধ্যে সারাক্ষণ ঝগড়া হচ্ছে। ও দিচ্ছে আমার দোষ আর আমি দিচ্ছি ওর দোষ। এক সময় বাবা ত্যক্তবিরক্ত হয়ে বলল, ‘ওঠ তোরা। এক্ষণ বাইততিগা বার হবি। চিপতে পারে না আম, হাতে লইয়া বইয়া রইছে।”
আমরা দুজনেই কল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে রাস্তায় চলে আসলাম। রাস্তায় এসে শাহাজাহান ভাবই বলে, ‘ঝামেলা কইরা ভালোই অইছে। নইলে হারাডা দিন যাইত এই ফালতু ছাগল লইয়া।’
আমরা বেশ মজা করে চা-সিগারেট খেয়ে ঘণ্টা দুয়েক পরে বাড়িতে গিয়ে দেখি ছাগলের গোস্ত রান্না হয়ে যাওয়ার পথে।
আমার বাসা ঢাকায়। স্ত্রী সরকারি চাকরি করে। দুইটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে আছে। আমাকে থাকতে হয় ফরিদপুর। ঈদের ছুটি শেষে আমি কলেজে চলে গেলাম। মেহতাব উদ্দিন মেথু কমিশনারের বাসায় ভাড়া থাকি।
সম্ভবত ৩রা জুন। আমি ক্লাসে। আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন ছাত্র এসে আমাকে বলল, ‘স্যার, আপনি ঢাকায় যান। আপনার ভাই অসুস্থ।’ আমাকে আর কিছু না বলে ও কোথায় উধাও হয়ে গেল! আমি ক্লাস থেকে বের হওয়ার পর আমার সহকর্মী কবি মাহবুব সাদিক বললেন, ‘মান্নান, আপনি ঢাকা চলে যান। প্রিন্সিপাল মহোদয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি চলে যান।’ এই সময় একটি হিম শীতল প্রবাহ আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বয়ে যাচ্ছিল। মাহবুব সাদিক স্যার যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আমার পাশে ছিল এমএ ক্লাসের ছাত্রী তানজিলা সিরাজী রুমা। রুমা কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজীর ছোট বোন। সে দ্রুত রিকসা নিয়ে আসে এবং আমাকে ফরিদপুর শহরে পৌঁছে দেয়। বিকেল তিনটার দিকে খিলগাঁয়ের বাসায় এসে দেখি শাহজাহানের লাশ। আমি কাঁদিনি। কাঁদতে পারিনি। আমার কেবলই মনে হয়েছে ভাবির কথা, তিনটি ছেলে-মেয়ের কথা। কী হবে এদের?
বড় ছেলে উপল ২০১৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিকম অনার্স এমকম পাশ করে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো একটি চাকরি করছে। মেজো মেয়ে উপম ইডেন কলেজে মাস্টার্স পড়ছে। ছোট মেয়ে স্বতি ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে একুশটা বছরের একটা দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করে এসেছি। কোনো দিন আমি আমার এই প্রাণের ভাইটিকে ভুলিনি। আমার সকল আনন্দে, সকল বেদনায় ও আছে আমার সঙ্গী হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের সকল আনন্দ-বেদনার আশ্রয়। যখনই আমার এই ভাইটির কথা মনে পড়ে তখনই মনে হয় ওই গানটির কথা : ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে…।”
চলবে…