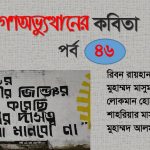সরকার আবদুল মান্নান
কত স্মৃতির ভিতর ধুলোর আস্তর জমে। একটু ফুঁ দিলে ভেসে ওঠে স্মৃতির পর্দায়। শার্সি টেনে দেখা যায় ঝলমলে রোদের ভিতর হাসছে আনন্দ-বেদনার রোদবৃষ্টি। দুঃখ-কষ্টের জমানো ব্যথা। বেড়ে উঠবার টানটান ঘটনা। আবার মিষ্টি ফুলের সুবাসও আসে জানালার ফাঁক গলে। ড. সরকার আবদুল মান্নান নিজের জীবনের সেইসব গল্পই ধুলোর চাদর সরিয়ে পাঠকের সামনে হাজির করছেন। নিজের জীবনের সাথেও তো মিলে যায় কত কিছু!
দুরন্ত বাতাসে :: এক
৮০ সালের কথা। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফুরফুরে মেজাজে আছি। সারাক্ষণ খালে-বিলে-পুকুরে মাছ ধরছি। পরীক্ষার জন্য মাছ ধরার নেশাটা চেপে রেখেছিলাম অনেক দিন। এখন পরীক্ষা শেষ। আমাকে আর রুখে কে! মাছের অত্যাচারে মা অস্থির হয়ে আছেন। খুব বিরক্ত হয়ে মা বলেন,
“এই হাইঞ্জা বেলা রাইজ্যের মাছ ধইরা আনলি। এহন আমি ক্যামনে সামলামু?’
বোনেরা আরও এককাঠি সরেস। বলে,
“তোর মাছ তুই কাটবি, তুই ধুবি, তুই রানবি।’ কেমন লাগে!
কিন্তু ঘরে যখন মাছ থাকবে না তখন আমার কি যে কদর!
মা বলেন, ‘যা বাজান, যা । দুইডা মাছ ধইরা লইআয়। পাতে দেওয়ার কিছু নাই।”
বোনেরা বলে, ‘এহে, এখন দাম দেহায়। যা, মাছ ধইরা আন।’
“মেছো’ রাশি বলে যদি কোনো রাশি থাকত তা হলে নির্ঘাত আমি হতাম ওই রাশির জাতক। মা জানেন, ধর্মজাল হোক, ঝাঁকিজাল হোক; ঠেলা আঁকড়া কোঁচ জুইত্তা পলো চালুন যা একটা হলেই হবে, আমি ঠিকই কিছু মাছ ধরে নিয়ে আসব। এমনকি শুধু হাত-পা নিয়ে পানিতে নামলেও চলবে। হাতিয়ে কিংবা ডুব দিয়ে হাতিয়ে হলেও নিশ্চয়ই মাছ ধরে নিয়ে আসব। কিন্তু বর্শি অসহ্য। জীবনেও বর্শি ফেলে বসে থাকিনি।
মাছ ধরার জন্য আমার সুনাম ছিল। আবার দুর্নামও ছিল। আপন ভাই-বোন কিংবা চাচাতো-জেঠাতো ভাই-বোনেরা যখনই আমার সঙ্গে ঝগড়া লাগত তখনই বলতো, ‘ওই মাউচ্ছা, জাউল্লা’ ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়। যাকে-তাকে মাউচ্ছা-জাউল্লা বললেই তো হবে না- চেহারা-সুরুতের সঙ্গেও তো বিষয়টা যেতে হবে। তাই মাউচ্ছা-জাউল্লা এর সঙ্গে মিলিয়ে বলত ‘কাউল্লা, পোড়া মরিচ’ ইত্যাদি। পোড়া মরিচও বলত না। বলত ‘পোড়া মইচ”। কেমন লাগে!
এর ব্যাখ্যায় আর আমি গেলাম না। যারা আমাকে চিনেন, বিশেষ করে দেখেছেন, তারা নিশ্চয়ই এইসব মধুসম্ভাষণের সানেনুজুল অনুধাবন করতে পারছেন। কিন্তু ছাই ফেলতে ভাঙা কুলার খোঁজ হয় চিরকাল। আমার ওই দুর্মুখ ভাই-বোনেরা, বিশেষ করে বোনেরা যখনই দরকার পড়ত তখনই ‘ল²ী ভাই’ বলে আমটা জামটা কলাটা পেঁপেটা ডাবটা পেয়ারাটা পেড়ে দেওয়ার বায়না ধরত।
কাদের জঙ্গলে গাব পেকেছে, বেতুম পেকেছে, বৈঁচি পেকেছে, এই খবর তাদের থাকত। আমার চাচাতো বোন রহিমা আপা বলত, ‘ও আমার সোনা ভাই গো”; আমার বড় বোন মাহমুদা আপা বলত ‘ও অমার কালা চাঁন”, ‘ও সোনা মাণিক’ আরও কত কি। তখনই আমি বুঝতাম ‘পোড়া মরিচে”র এখন খুব দরকার। পটানোর এই দরদি ভাষায় আমি ঠিকই মুগ্ধ হতাম এবং ওদের আবদার শুনতাম। ওদের পটানো আমার ভালোই লাগত।
এইসব করে করে এবং অধিকাংশ সময় লাফাঙ্গাদের মতো আড্ডা দিয়ে ও গ্রামময় ঘুর বেড়িয়ে দুর্দান্ত সময় পার করছিলাম আমি। বিশেষ করে সুন্দরী ক্লাসমেটদের এবং জুনিয়রদেরও খোঁজখবর বেশ আগ্রহের সঙ্গেই নিচ্ছিলাম। কখনো কখনো কারো কারো ক্ষেত্রে এইসব খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়টা দৃষ্টিকটূ ঠেকছিল, শোভনতার সীমাও মানা হচ্ছিল না। কিন্তু কী করা যায়!
এরই সূত্র ধরে বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু এবং তস্য বন্ধু করে করে বন্ধুদের সীমাও অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু বিনয়ী মানুষ ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে আমার কিছুটা পরিচয় সর্বত্র ছিল বলে লোকেরা দেখেও না দেখার এবং শুনেও না শোনার মতো থেকেছে। সেই সুযোগে সময় যে এত মধুর হয়ে উঠতে পারে তা আগে কখনোই অনুভব করিনি।
এর মধ্যে একদিন এসএসসির রেজাল্ট দিয়ে দিল। আমি সেকেন্ড ডিভিশন পেয়ে পাস করেছি। শুধু তাই নয়, গাধাদের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা হলে যেমন একটি নিশ্চয়ই ফাস্ট হবে, আমিও তেমনি ৮০র এসএসসি পরীক্ষায় এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ফাস্ট হলাম। এবং একেই বলে গাধাশ্রেষ্ঠ।
যারা ওই বছর এসএসসি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি, প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় ওরা পঁচিশে পঁচিশ করে নম্বর পেয়েছে। আমি পেয়েিিছ ঊনিশ নম্বর করে। ওই নম্বরটুকুর জন্য ৮০ সালের এসএসসিতে কেউ প্রথম বিভাগ পায়নি। বলে রাখি, এখলাসপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ল্যাব. তখন খুবই সমৃদ্ধ ছিল। কখনোই আমি প্রাকটিক্যাল মিস করিনি।
পরীক্ষা থেকে পাস- এই সময়ের মধ্যে বইপুস্তক আর ধরা হয়নি এবং এর পর আরও পড়াশোনা করব কি না, এই নিয়ে কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। কিন্তু বাবা খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। বিশেষ করে টাকাপয়সা ছাড়া কোথায় পড়ানোর সুযোগ আছে, এইসব। খোঁজ তিনি পেয়েছেন একটু দেরিতে। নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজে ৮০ সাল থেকে শুরু হয়েছে সরকারি কার্যক্রম। বাবা কার কাছ থেকে শুনেছেন, ওখানে প্রায় বিনে পয়সায় পড়ার সুযোগ আছে।
একদিন পরে আমাকে নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে। লুঙ্গি পরে নিশ্চয়ই কেউ কলেজে যায় না। স্কুলে আমরা লুঙ্গি পরেই যেতাম। মেয়েরা যেত শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ পরে। তবে সিক্স-সেভেন পর্যন্তই সালোয়ার-কামিজ চলত। তার পর সব মেয়েই শাড়ি পরত। সেটাকে শাড়ি পরা বলা যায় না। কোনো রকমে শাড়ি গায়ে প্যাচিয়ে চলে আসা। কারো শাড়ি মাটি লেচড়িয়ে যেত, আর কারোটা হাঁটু অবধি উঠে যেত। সিক্স-সেভেন পর্যন্ত ছেলেরা লুঙ্গি কিংবা হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে আসত। কিন্তু এইটে উঠলে প্রায় সবাই লুঙ্গি পরিধান করত। ফুল প্যান্ট পরে স্কুলে আসার সংস্কৃতি ও আধুনিকতা তখনো তৈরি হয়নি। জুতা বা স্যান্ডেলের প্রচলনও তেমন ছিল না। বই খাতা বহন করার জন্য ব্যাগ ব্যবহার করতেও দেখিনি কাউকে। সবাই হাতে ও বগলে করে বই খাতা বহন করতাম। কলেজে কী ব্যবস্থা, জানা নেই। তবে লুঙ্গি পরে যে কলেজে যাওয়ার যায় না সেটা অনুভব করেছিলাম। সুতরাং বাবাকে বললাম, আমার তো প্যান্ট নেই।
বাবা দেরি না করে আমাকে নিয়ে গেলেন বামের বাজারে হাসন খলিফার কাছে। এই হাসন খলিফা আমার জেঠাতো বোনের স্বামী এবং খুবই জনপ্রিয় দর্জি। একদিনে সে আমাকে প্যান্ট বানিয়ে দিল। পরদিন বাবা আমাকে নিয়ে তোলারাম কলেজে চলে এলেন।
আমাদের বাড়ি থেকে তখন এখলাসপুর লঞ্চঘাট তিন-চার কিলোমিটার দূরে। ফসলের মাঠের আল দিয়ে হেঁটে ওই পথ অতিক্রম করতে হতো। বহুবার আমি বন্ধুদের সঙ্গে লঞ্চঘাট এসেছি। আমার ক্লাসফ্রেন্ড কামালের চাচাতো ভাই বিল্লাল ও তার কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল এই লঞ্চঘাট এলাকার হোমড়াচোমরা ব্যক্তি। সুতরাং কামালের সঙ্গে এই এলাকায় আসতাম আড্ডা দিতে। মুজিব, নেসার, বাবুল, জাহাঙ্গীর, মুনির এবং আরও অনেক বন্ধুদের সঙ্গে এই এলাকায় বহুবার এসেছি। কিন্তু লঞ্চঘাট এসে এই প্রথম মনে হলো আমি বেশ বড় হয়ে গেছি। গ্রাম থেকে কলেজে পড়তে যাওয়ার যুবক তখন খুব বেশি ছিল না। আমি সেই বিরল সৌভাগ্যবান যুবকদের একজন।
লঞ্চের ভাড়া খুব কম দিতে হবে বলে বাবা ডেকে গিয়ে বসলেন। ওখানে গরিব লোকেরা বসে। মেশিনের বিকট শব্দে ওই ডেকের যাত্রীরা কেউ কারো স্বাভাবিক কথা শুনতে পায় না। সুতরাং সবাইকে চিৎকার করে কথা বলতে হয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিষ্ঠাতে না পেরে আমি উপরে কেবিনের সামনে চলে আসলাম।
আজকের মতো তখন সারি সারি লোহার টুল পেতে কেবিন বানানো ছিল না। তখন চার-পাঁচটি রুম করে প্রত্যেক রুমের দুই পাশে মুখোমুখি বসার জন্য সোফার ব্যবস্থা ছিল। সোফা বলতে কাঠের বেঞ্চের উপর সোফার মতো আবরণ লাগানো থাকত। অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীরা ওই কেবিনে বসতেন। সাধারণ মানুষ কেবিনে ঢুকত না। অবশ্য নব্বইয়ের দশকে এসে ওইসব কেবিনে যখন কৃষক শ্রমিক পোশাক শিল্পী থেকে শুরু করে সবাই গণহারে বসতে শুরু করে তখন ওই কেবিন উঠিয়ে দিয়ে গণরুম বানিয়ে দেওয়া হয়। এখনো ওই অবস্থায় আছে। আমি ওই কেবিনের চারদিকে ঘোরাঘুরি করে এবং কখনো বা লঞ্চের পিছনেকখনো বা লঞ্চের পিছনে নামাজের স্থানে বসে থেকে তিন ঘণ্টা সময় পার করে দিলাম।
মেঘনা বিশাল নদী। দুই তীর যেন দুই দেশ। এক পাড়ের জীবন ও জগতের সুখ দুঃখ আশা আকাক্সক্ষার সঙ্গে অন্য পাড়ের জীবন ও জগতের কোনো সম্পর্ক নেই। লঞ্চ ঘাটে এসে না ভিড়লে মেঘনা নদীর মাঝ থেকে তীরের সৌন্দর্য নিবিড়ভাবে উপভোগ করাও সম্ভব নয়। বিশেষ করে পশ্চিম পাড়ের প্রকৃতি ও জীবন লঞ্চ থেকে দেখা বা অনুভব করা একেবারেই অসম্ভব। শুধু নদীতে নিত্য বহমান যে জীবন- বিচিত্র নৌকায় জাহাজে স্টীমারে ট্রলারে কিংবা ট্যাঙ্কারে তার একটি দূরাগত আহবান অনুভব করতে পারবেন।
ইঞ্জিন চালিত নৌকার প্রচলন তখন ছিল না। এখন যে ইঞ্জিন চালিত অসংখ্য নৌকার বিকট শব্দে নদীর নিস্তব্ধতার আনন্দ ও সৌন্দর্য চিরতরে শেষ হয়ে গেছে , তখন তা ছিল না। বিচিত্র রঙের কাপড় জোড়া দিয়ে তৈরি পালতোলা নৌকাই ছিল তখন নদীর চিরায়ত সৌন্দর্য। নদীতে বাতাস থাকলেই হলো। সেই বাতাস যেদিক থেকেই প্রবাহিত হোক না কেন। বিস্ময়কর দক্ষ মাঝিরা পাল তোলার বিচিত্র কৌশল ব্যবহার করে সে তার লক্ষ্যের দিকেই নৌকা নিয়ে যেতে পারত। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার জো নেই যে বাতাস যে দিক থেকে বইছে কৌণিকভাবে প্রায় সেদিকেই নৌকা নিয়ে যাচ্ছে মাঝিরা। আমি মাঝিদের মধ্যে এই বিস্ময়কর বিজ্ঞানবুদ্ধি দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এই ধরনের পরীক্ষা অনেক সময় বিপদের আশঙ্কা তৈরি করে। কোনো কোনো নৌকা চলছে বৈঠা বেয়ে বা দার টেনে। ওই নৌকায় নেতা মাঝিটি হাল ধরে বসে থাকে। নদীতে অনুকূলে বাতাস না থাকলে কিংবা স্রোতের বিপরীতে যেতে হলে মালবাহী নৌকাগুলো গুণ টেনে নিয়ে যেতে হয়। নৌকার মাস্তুলে লাগানো গুণ তীর থেকে যারা টেনে নিয়ে যায় তাদের কষ্টের কোনো সীমা থাকে না। নদীর তীরে খাল বিল পুকু জঙ্গল পায়খানা বেতবন কাশবন যাই থাকুক না কেন সবকিছুকেই অতিক্রম করে যেতে হয় গুণটানা মাঝিদের।
মাছ ধরার নৌকাগুলো খুব ছোট। দূর থেকে মনে হয় এই বুঝি তলিয়ে গেল। কিন্তু না। ঢেউয়ের আড়াল থেকে ঠিকই ভেসে ওঠে। আর ঢেউয়ের ডগায় দোল খায়। দূর থেকে মাছুয়াদের মনে হয় তালপাতার সেপাই কিংবা ফসলের মাঠে দাড় করিয়ে রাখা কাকতাড়ুয়া। এদের মধ্যে খুব কম বয়সী ছেলেছোকরারাও আছে। এরা ভীষণ সাহসী। দুর্দান্ত নদীর বুকেই এদের নিত্য বসবাস। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এরা জাল পেতে রাখে। সেই জালের সঙ্গে ঝোলানো থাকে নানা রঙের প্লাস্টিকে বল। ওই বলগুলো একদিকে জাল ধরে রাখে এবং অন্য দিকে জলযানগুলো জালের অবস্থান বুঝতে পারে।
চরের আড়ালের প্রায় বদ্ধ জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য জাগ পেতে রাখা হয়েছে স্থানে স্থানে। জলের তলে অনেকটা জায়গা জুড়ে আমগাছের, হিজল গাছের ডালপালা দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে এবং ডালপালাগুলোকে এক জায়গায় আটকে রাখার জন্য স্থানে স্থানে বাঁশ পুতে পুতে তার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাঁশগুলো একদিকে পানির সমান্তরালে একটিকে আরেকটির সঙ্গে টেনে এনে বেঁধে রাখা হয়েছে আবারা একইভাবে মাথাগুলোও বেঁধে রাখা হয়েছে। দূর থেকে মনে হয় অসংখ্য ধনুক দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। উপরে আছে ঘনবদ্ধ কচুরিপানা। নিরাপদ আশ্রয় ভেবে মাছেরা যখন এই জায়গাটিতে বিপুল পরিমাণে বসবাস শুরু করবে তখনই একসময় চারদিক থেকে জালের বেড় দিয়ে মাছগুলো আটকানো হবে।
লঞ্চে দেখলাম খালাসি সুকানি বাবুর্চি মাস্টার টিকেট মাস্টার এবং ডকে ইঞ্জিন ঘরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা মেশিন ম্যান। এই বিপুল মেঘনার বুকে এদের বসার জন্য এবং বিশেষ করে শোবার জন্য যে স্থান সংকুলান করা হয়েছে তা অমানবিক। বাবুর্চি যেখানে রান্না করে, লঞ্চের সেই পিছনের জায়গাটিতে চুলার স্থান অতি সংকুচিত। ওই চুলায় কোনো রকমে হাড়ি পাতিল ঢোকান যায়। সেখানেই ঝোলানো থাকে বাবুর্চির তেলচিটকানো লুঙ্গি, তিল পড়া সার্ট, গেঞ্জি, আন্ডার ওয়ার। আর তার পাশে ওই বাবুর্চির রাত্রিযাপনের জন্য যে স্থান সংকুলান করা হয়েছে ঈশ্বরের পৃথিবীতে মনুষ্যবাচক প্রাণীর জন্য আর কোথাও এত সংকীর্ণ জায়গার ব্যবস্থা আছে কি না আমার জানা নেই। তার পাশে মাটির গামলা ভরা পানি। প্লাস্টিকের মগ বেঁধে রাখা হয়েছে গামলার সঙ্গে। যাত্রীরা গামলা থেকে মগ ভরে ভরে জল খায়। ওখানেই আচে চা সিগারেট ও বিস্কুটের দোকান। তার উলটো দিকে দুটি পায়খানা। ময়লা যায় সরাসরি নদীর জলে। শত বছর ধরে এই-ই চলে আসছে।
অতি সংকীর্ণ এই জায়গাটিতে সারাক্ষণ যাত্রীরা দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ চা সিগারেট খাচ্ছে, কেউ হাওয়া খাচ্ছে আর অনেকে লাইন ধরে আছে পায়খানায় যাওয়ার জন্য। উপরে কেবিনের পাশে মাস্টারের জন্য নির্ধারিত স্থানটির অবস্থাও তথইবচ। এইসব দেখে দেখে কখন যে নারায়ণগঞ্জ লঞ্চঘাটে চলে এসেছি বুঝতে পারিনি। বাবাও আমাকে নিয়ে নেমে যাওয়ার জন্য ডক থেকে উপরে চলে এসেছেন।
লঞ্চঘাট থেকে হেঁটে আমরা চলে গেলাম তোলারাম কলেজে। হাঁটা যে বাবার কত প্রিয়, ছোট বেলা থেকেই আমরা তা জানি। আর নারায়ণগঞ্জ তো নস্যি, ঢাকার এহেন কোনো জায়গা নেই বাবা চিনেন না। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তিনি দোকানে লেখা ঠিকানা পড়বেন, সাইনবোর্ড পড়বেন। কোথায় স্কুল কলেজ মাদরাসা মসজিদ মার্কেট বাজার হাসপাতাল অফিস আদালত সব তিনি চিনে নিবেন। তিনি প্রায় চোখ বন্ধ করে আমাকে তোলারাম কলেজে নিয়ে গেলেন।
কলেজ গিয়ে শুনলাম এইচএসসিতে ভর্তিকার্যক্রম শেষ। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। বাবা খুব হতাশ হয়ে পড়লেন। এমন সময় বিএ ক্লাসে পড়ুয়া একজন পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে আমদের দেখা হয়। সে পরামর্শ দেয় কলেজ ছাত্রসংসদের জিএস জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য। শুরু হলো জাহাঙ্গীর ভাইকে খোঁজার পালা। কিন্তু কলেজের কোথায়ও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত বাবা আর আমি পাইকপাড়া তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার বাড়ি খুঁজে পেতে কিছুমাত্র অসুবিধা হলো না। পাইকপাড়ার সবাই ওই বাড়িটি চিনে। জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো।
জাহাঙ্গীর ভাই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করলেন। অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা হলো। তিনি আমার পড়াশোনা এবং আমাদের পারিবারিক অবস্থার খোঁজখবর নিলেন। প্রথাগত ছাত্রনেতাদের উন্নাসিকতা, দাম্ভিক্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, দায়িত্বহীনতা কিছুই তার মধ্যে লক্ষ করা গেল না। তখন দুপুরের খাবার সময় প্রায় পেরিয়ে গেছে। জাহাঙ্গীর ভাই আমাদের না খাইয়ে ছাড়লেন না। তিনি বাবাকে চাচা বলে সম্বোধন করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, ‘চাচার থাকার দরকার নেই। উনি বাড়িতে চলে যাক। তুমি থাক। একটা কিছু করতে পারি কি না দেখি।”
বাবা বাড়িতে গেলেন না। আমারা বুড়িগঙ্গা নদী পাড় হয়ে বক্তাবলি চলে গেলাম। ওখানে আমার জেঠা করিম মাস্টার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। উনি একটি বাড়িতে লজিং থেকে শিক্ষকতা করেন। ওই বাড়িতে আমি প্রথম গোরুর ভুঁড়ি খাই। বিস্ময়কর সুস্বাদু এই এই জিনিস কী করে রান্না করা হলো তার পদ্ধতি কিছুই জানা হলো না। আমাদের অঞ্চলে গোরুর ভুঁড়ি ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হতো। শকুনে খেতো। এখন মনে হয় দেশের সর্বত্রই এই সুস্বাদু ভুঁড়ি খাওয়া হয়। পরদিন সকালে ওই বাড়ি থেকে আমরা বের হয়ে আসি। বাবা চলে যান গ্রামের বাড়িতে আর আমি দেখা করি কলেজে জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সঙ্গে।
কলেজে গিয়েই জাহাঙ্গীর ভাইকে পেয়ে যাই। উনি আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে দেখা করতে যান। কয়েক মিনিট পর বের হয়ে এসে আমাকে বললেন, তুমি এখানেই দাঁড়াও। স্যার তোমাকে ডাকবেন।
আমি দাঁড়িয়ে আছি। স্যারের পিওন আমার খোঁজখবর নিচ্ছে। এমন সময় আমার ডাক পড়ল। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রুমে ঢুকলাম এবং বিনয়ের সঙ্গে স্যারকে ছালাম দিলাম। রুমে ঢুকে দেখি আরও কয়েকজন শিক্ষক বসে আছেন। স্যারকে দেখে আমি রীতিমতো মুগ্ধ। স্যুটকোট পরা অসাধারণ সুদর্শন মানুষ। দেখলেই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয় এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
স্যার আমাকে ইংরেজিতে তিনটি প্রশ্ন করলেন। আমি ইংরেজিতেই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলাম।
পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, এ প্রায় অবিশ্বাস্য। স্কুল জীবনে কৌতূলবশত কিছু দিন আমি ইংরেজি গ্রামার ইংরেজিতেই শিখেছিলাম। আর প্রিন্সিপাল স্যার ওই প্রশ্নগুলোই আমাকে করেছেন। বলা যায়, আমি একশতে একশই পেয়ে গেলাম। তার পর প্রশ্ন করা রেখে প্রিন্সিপাল স্যার ও অন্যান্য স্যারেরা আমার হাঁড়ির খবর নিতে শুরু করলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। কিন্তু অমানবিক যুদ্ধটা শুরু হয় তার পরে। আমার জীবনের এই মোড় পরিবর্তনের আখ্যানটুকু লেখা খুব কষ্টসাধ্য। তবুও লিখব।
[চলবে]