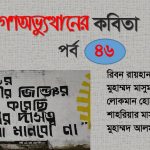চিত্র: গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়ের স্কুলে যাওয়া (প্রতীকি ছবি)
প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম সত্তরের দশকে। স্কুলে তখন গ্রাম নিয়ে রচনা লিখতে হতো- ‘তোমার গ্রাম’।
আমরা বই থেকে মুখস্থ করে লিখে দিতাম। শিক্ষকগণ পড়তেন। নম্বর দিতেন। তাঁরা কখনোই মনে করতেন না যে, এতে কোনো ভুল হচ্ছে। শিক্ষকগণ যে গ্রামে থাকতেন আমরাও তো সেই গ্রামেই থাকতাম। কিন্তু আমরা যে গ্রাম নিয়ে রচনা লিখছি সেই গ্রাম তো আমাদের নয়। শিক্ষকগণ আমাদের এই ভুল ধরিয়ে দিতেন না। আমাদের ঘিলুতেও আসত না যে, যে গ্রাম নিয়ে রচনা লিখছি ওই গ্রাম তো আমার গ্রাম নয় কিংবা আমাদের গ্রাম নয়। ওই গ্রাম তো আমরা চিনি না। আজ এত দিন পরে মনে হচ্ছে, যে গ্রামটা আমাদের ছিল, যে বাড়িটা আমাদের ছিল, সারাটাক্ষণ যে বাড়িতে, যে গ্রামে হৈহৈ রৈরৈ করে বেড়িয়েছি, গাছে চড়েছি, খালে বিলে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছি, মাঠে ঘাটে উঠানে বিচিত্র খেলা নিয়ে মত্ত থেকেছি, সেই বাড়ি, সেই গ্রাম নিয়ে তো কখনোই একটি রচনা লিখিনি।
আজ সেই ঘর-বাড়ি, গ্রাম, সেই জনপদ আর নেই। নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাতাসের ভেতরে থেকে যেমন বোঝা যায় না, প্রতিটি নিঃশ্বাস কত মূল্যবান, তেমনি শৈশবে গ্রামের আলো-বাতাসে বেড়ে উঠে বুঝিনি যে, গ্রামটা কত প্রাণের জিনিস, কী অপরিসীম তার মায়ার টান। ফলে নিজের ঘর-বাড়ি নিয়ে, গ্রাম নিয়ে, অঞ্চল নিয়ে কোনো দিন কিছু লেখা হয়নি।
তারপর অনেকগুলো দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। ঘর নেই, বাড়ি নেই, গ্রাম নেই। উদ্বাস্তু এক জীবন।
টঙ্গী, কাপাসিয়া, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ফরিদপুর, খিলগাঁও করে করে একটা জীবন পার করে দিলাম। কোথাও বিন্দুমাত্র শিকড়ের আস্বাদ পেলাম না।
কত বছর ধরে খিলগাঁও আছি। প্রতিবেশীরা আছে বহুদিন ধরে। একই বিল্ডিংয়ে অথবা আশেপাশের বিল্ডিংয়ে। তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই হলো না। তারা আত্মীয় নয়, অনাত্মীয় নয়, শত্রু নয়, মিত্র নয়, আপন নয়, পর নয়। কিছুই নয়। সম্পর্কহীনতার এমন আজব জীবন বাংলাদেশে কী করে সম্ভব, ভেবে পাই না।
বহুদিন ধরে আমি এমন এক আজব জীবন বহন করে চলছি। মনে হয়, আমার মতো অনেকেই। এ যেন অনতিক্রম্য নিয়তি। ভেতরে যেন একটি কান্না জমে জমে পাথর হয়ে গেছে। এর থেকে কোনো মুক্তি নেই। পরিত্রাণ নেই।
খুব মনে পড়ে শৈশবের দিনগুলোর কথা। দশ গ্রামে এমন বাড়ি কমই আছে যখানে অবলীলায় ঢুকে পড়া যেত না। এমন কোনো ঘর কমই আছে যেখানে আদর-আপ্যয়ন ছিল না। গাছগোড়া আর লতাপাতার সম্পর্ক নেই এমন কোনো বাড়ি কল্পনাও করা যেত না। “তুই ওমকের পুত না?” ‘‘তুমি ওমকের পোলা না”? ‘‘তুমি ওমকের ছেলে না”? বলে চৌদ্দ গোষ্ঠীর খবর নিয়ে শুরু হতো আদর আপ্যায়নের পালা। আদর-আপ্যায়ন মানে পোলাউ-কুর্মা খাওয়ানো নয়। ঘরে যা আছে তাই এনে সামনে দেওয়া। সিদ্ধ একটা মিষ্টি আলু, চালভাজা, দুটি পেয়ারা, একটি পাকা গাবও হতে পারে।
কিন্তু কেন লিখছি এইসব কথা? কী হবে এইসব লিখে? আর কি কোনোদিন ফিরে পাব হারিয়ে যাও বাড়ি-ঘর, গ্রাম-গঞ্জ, পাড়াপ্রতিবেশি, আত্মীয়স্বজন?
কোনোদিন না।
তবুও এতদিন পরে মনে হচ্ছে, হৃদয়ের ক্যানভাসে যে ঘর-বাড়ি-গ্রাম ও জনপদ আঁকা হয়ে আছে তার কিছু রং আর কিছু রেখা আখরে বেঁধে দিলে কেমন হয়! ভেতরে জমে থাকা কান্নার উপলখণ্ডে কি একটু স্রোত বইবে?
জানি না।
আর সে জন্যই সাহস পাই না লিখতে। নিজের উপর আস্থারও বড় অভাব। সত্যিকার চিত্রটা যদি আঁকতে না পারি! যে চিত্রটাতে বেদনার রংটাই প্রগাঢ়, তা যদি আঁকতে না পারি তা হলে কী হবে! তার চেয়ে বরং হৃদয়ের কন্দরে যে চিত্রটা আঁকা আছে তাই থাক। ওকে আর দীনহীন করে লোক-সম্মুখে হাজির করে হাস্যকর করে তোলার কোনো মানে হয় না। এবং অন্যদিকে “কে হায় হৃদয়খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?” সত্যি কি কেউ কারো কষ্টের ঐশ্বর্যকে অনুভব করতে পারে? অন্যের বেদনার রঙে রাঙিয়ে তুলতে পারে নিজেকে?
জানি না।
এতসব দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরেও শরণ নিতে হয় গ্রিক ট্রাজেডির সেই বিখ্যাত অনুভব “ক্যাথারসিস” বা আবেগ বিরেচন তত্ত্ব। এ হলো উত্তরণের আশ্রয়, দুঃখ হজম করার মহৌষধ- পারগেশন। আমিও সেই আশ্রয়টুকু নিতে চাই।
ছাগল খুঁটি বলে একটা কথা আছে। ছাগল টানলে- বিশেষ করে পানিতে নামাতে গেলে বোঝা যায় ছাগল খুঁটি কাকে বলে। সামনের দুই পা মাটিতে এত শক্ত করে আটকে রাখে যে, কিছুতেই নাড়ানো যায় না। যেন খুঁটি গেড়ে রেখেছে। অগত্যা কোলে করে নিয়ে পানিতে নামিয়ে দিতে হয়। তার পরেও ঝেড়ে দৌড় দিয়ে বাড়িতে চলে আসে। শীতকালে গ্রামের শিশুদের অবস্থাও ছাগলের মতোই।
সারাদিন স্বল্প পানির নালা-নর্দমা সেঁচে মাছ ধরে ধরে দিন কাবার। শরীরময় কাদা মেখে বিকেলে যখন ভূতের মতো চেহারা নিয়ে মার সামনে দাঁড়াতাম তখন তার অগ্নিমূর্তি দেখে কে! মারবেন না কাটবেন বুঝতে না-পেরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতেন পুকুর-ঘাটে।
পানিতে নামতে চাইতাম না কিছুতেই। ভীষণ ঠাণ্ডা পানি। আর ঠাণ্ডা হবেই না বা কেন? পুকুরের চারপাশে গাছ আর গাছ। রোদ পড়ার ফাঁক নেই বিন্দুমাত্র। তারপর পুকুর ভর্তি কচুরি। ঘাটের সামনে সামান্য জায়গা ছাড়া কোথাও খালি নেই একটুও। এই সন্ধ্যায় উত্তরের এই পুকুরের পানিতে নামলে শরীরে সাপে-কাটার যন্ত্রণা হবে। মা পানিতে নামানোর জন্য চেষ্টা করতেন। আর আমি ছাগল-খুঁটি ধরে থাকতাম। অগত্যা মা কোলে করে পানিতে নামিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। আর আমি জটপট মার গা বেয়ে এতটা উঠে যেতাম যাতে শরীরে পানি না লাগে।আর মাকে এত মজবুত করে চেপে ধরতাম যে, “আমাকে পানিতে নামাতে গেলে আপনাকেও নামতে হবে।”
অগত্যা মা আর চেষ্টা করতেন না। সেই যে গা বেয়ে উঠেছি সে ভাবেই বাড়িতে নিয়ে এসে গরম পানি দিয়ে ঘষে-মেজে গোসল করিয়ে দিতেন। তার পর পরনের শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিতেন শরীর। সারা গায়ে মেখে দিতেন সরিষার তেল।
সন্ধ্যায় হাফ প্যান্ট, ফুল তাহার শার্ট আর চাদর গায়ে দিয়ে মার কাছে গিয়ে বসতাম পিড়ি পেতে। মা তখন বৈকালিন রান্না করছেন। শীতের বিকেলে চুলার লাল আগুনের ছায়া পড়ত মার মুখে। কি যে সুন্দর লাগত মাকে! মনে হতো, এই আমার মা! কেমন অপরিচিত সুন্দর! এত সুন্দর মানুষ হয় কখনো? একদিন বলেও ছিলাম ‘মা, আমনেরে অনেক সুন্দর লাগতেছে।’
মা খুব লজ্জা পেয়েছিলেন। আর আমাকে কোলে নিয়ে মা অনেক চুমু খেয়েছিলেন। এখন মনে হয়, লজ্জা লুকোতেই মা আদরের আশ্রয় নিয়েছিলেন।
জলের স্বভাব আমরা বেশ বুঝতাম। রোদের জল, ছায়ার জল, গভীর জল, হালকা জল- কত রকমের ওই জলের সঙ্গে ছিল আমাদে নিত্যদিনের খেলা। কখন কোন জলের সঙ্গে সখ্য পাতাতে হবে, তা নিয়ে ভাবতে হতো না কখনই। শীতে ঝোপঝাড়ের নিচে উত্তরের পুকুরে ভুলেও যেতাম না আমরা।
গৃহবধূ আর কন্যারা যেত তখন। কাঁখে কলসি নিয়ে পুকুর-ঘাটে গিয়ে কলসির তল দিয়ে পানিতে ঢেউ তুলত তারা। জল পরিষ্কার করে কলসিতে জল ভরার এই দৃশ্য সব সময়ের। তারপর ভরা কলসির মুখ নেড়ে পানি কমিয়ে নেওয়া হতো যাতে কলসি কাঁখে চলার সময় পানি পড়ে গা ভিজে না যায়। কখনো কখনো ঘাটে বসে সুখ-দুঃখের গল্প-পাতা।
ওই কালো জলে কাজ ছিল না আমাদের। আমরা যেতাম দক্ষিণের খোলা প্রান্তরের নয়া পুকুরে; যেতাম বিলের দিকে উঠে যাওয়া খালের জলে। সেই জল ছিল হালকা। অল্প তাপেই গরম। দুপুরের দিকে গ্রামের শিশু-কিশোরদের লম্ফ-ঝম্ফ সাঁতার ছিল এই সব জলে। পুকুরের একদিকে ছিল আমাদের রাজত্ব, আর অন্য দিকে কৃষকরা গুরু-ছাগল গোসল করাত। আইল্লা (আলী রাজা) কখনো কখনো গরু গোসল করাতে এসে গরুর পিঠে চড়ে বসত। পিঠে বসে বসেই গরুটির গা মেজে দিত খর-বিচালি দিয়ে। আমিও একদিন বায়না ধরেছিলাম পুকুরে গরুর পিঠে চড়ব। আইল্লা রাজি হলো। কিন্তু গরুটি এতই বজ্জাত, আমাকে নেবেই না পিঠে। আইল্লার সঙ্গেই ওর যত ভাব।
কখনো কখনো দেখি, শীতের সকালে রোদ পোহানোর সময় গরুটি আইল্লার পিঠ চেটে দিচ্ছে। আইল্লাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘কেমন লাগেরে?’
সে বলল, ‘ভালা, খুব ভালা। একটু কুতকুতানি অয়।’
অনেক বার আমি আইল্লার পাশে পিঠ উদাম করে বসেছি- গরুটা যদি একবার জিহবা দিয়ে আমার পিঠ চেটে দেয়। কিন্তু আইল্লার গরুটা কখনই তা করেনি। পিঠে কুতকুতানির স্বাদ আমি কখনই পাইনি। আইল্লা কাতুকুতুকে বলত কুতকুতানি।
গ্রীষ্মে পুকুরের পানি একেবারেই কমে যায়। খালগুলো যায় শুকিয়ে। সেই বুক সমান পানিতে ডুব দেওয়ার সুযোগ তখন থাকত কম। লম্ফ-ঝম্ফেরও সুযোগ তেমন থাকত না। তবুও পাড়ার সব বালক-বালিকা গিয়ে জুটতাম সেই সামান্য পানিতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানিতে চলত উৎসব। পানি ঘোলা করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে উঠত যে, এক সময় তা কাদাজল হয়ে উঠত। সাঁতার কাটা, চিৎ হয়ে কিংবা ওপুর হয়ে জলে ভাসা, বল খেলা, ছোঁয়াছুয়ি খেলা -এই সব করতে করতে এক সময় দুপুর গড়িয়ে যেত। ছোট কাকু বলতেন, ‘‘ডুবা, ডুবা। ভালা কইরা ডুবা। একজনেরে ধইরা আরেক জনে চুবা। নইলে খেলা কী?’
ঝগড়া বাধানোর ওস্তাদ ছোট কাকুকে আমরা খুব পছন্দ করতাম। আমাদের এক জন বলে মনে করতাম। তিনিও মাঝে-মধ্যে আমাদের সঙ্গে নেমে যেতেন পানিতে। আমরা তার কোলে-কাঁধে উঠে উঠে রীতিমতো গাছ তৈরি করতাম। তারপর সেই গাছ ভেঙে পড়ত পানিতে। এও ছিল একটা খেলা।
একবার কাকুর সঙ্গে আমরা সবাই খেলছি। পুকুরের জলে জলের উৎসব। জল তীরে তুলে ফেলার মতো অবস্থা। হৈচৈ-চিৎকার-চেচামেচি তো আছেই। এমন সময় দেখা গেল পুকুরের পারে একটি শিশুর পায়ে ধরে কাকু আকাশ-পাতাল ঘুরাচ্ছেন আর শিশুটির নাকমুখ দিয়ে পানি বেরোচ্ছে। পুকুর থেকে আমরা উঠে আসলাম সবাই।
কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে চিৎকার করতে লাগলাম। পরে জানলাম, সবুর হোসেন সবার দেখাদেখি পানিতে নেমে পড়েছিল খেলতে। কিন্তু সে খুবই ছোট। সাঁতার জানে না। সে পানিতে তলিয়ে যাচ্ছিল আর হাবুডুবু খাচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ সে হাত-পা নেড়ে চেষ্টা করছিল বাঁচার। এমন সময় কাকুর চোখে পড়ে। তখন তার তলিয়ে যাওয়ার অবস্থা। কাকু দেখেন, নাকে-মুখে পানি গিয়ে পেট ঢোলের মতো হয়ে গেছে তার। বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা বোঝার আগেই তিনি সবুর হোসেনকে পা ধরে ঘুরিয়ে পেটের সব পানি নাক-মুখ দিয়ে বের করে দেন। সবুর হোসেন বেঁচে যায়। কাকু গ্রামে রীতিমতো নায়ক হয়ে উঠলেন। আর আমাদের কাছে মহানায়ক। কাকুর সঙ্গে থাকা মানে একজন সেলিব্রেটির সঙ্গে থাকা। অহংকারে আমাদের পা মাটিতে লাগে না যেন।
শুধু আমি নই। কিংবা গফুর, নবু, বা রহিমা নয়- কাছে-পিঠের পাঁচ-ছয়টি বাড়ির শিশুরা সাঁতার শিখেছে কাকুর কাছে। চার-পাঁচজন শিশুকে হাটু পানিতে নামিয়ে দিয়ে তিনি বলতেন, ‘হাঁট, পানিতে হাঁট। পানিতে হাঁটলে পানির ভয় কমবো। তারপর হাতরের কতা।’
পানিতে একটু হেঁটেই আমরা বলতাম, ‘কাকু পানিরে ভয় পাই না। এখন হাতর শিখান।’
কাকু আমাদের জলের উপর ভাসিয়ে দিয়ে আলতো করে পেটের নিচে হাত দিয়ে রাখতেন। আর আমরা জোরেশোরে হাত-পা ছুড়তে থাকতাম। এক সময় কাকু আমাদের তার পিঠে চড়িয়ে পুকুরময় সাঁতার কেটে আসতেন। আমরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে চিৎকার-চেচামেচি করতাম। আবার আনন্দও পেতাম। এভাবে কাকুই আমাদের জলের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে দেন। তার পর দুই হাতের বগলের নিচে কলা গাছ রেখে সাতাঁর কাটা কিংবা কলসির তলে ভর করে সাতাঁরের চেষ্টা করেছি।
জ্যৈষ্ঠের জলের মতো জল আর হয় না। এই জল দুষ্টু জল, এই জল মিষ্টি জল, এই জল শান্ত জল, প্রাণে ভরা জল। জ্যৈষ্ঠের তরুণ জল তরতর করে যখন খেত-খামারের দিকে বয়ে যেত, তখন আমরা সেই দুরন্ত স্বচ্ছ জলের সঙ্গে খেলতাম। ওর বয়ে যাওয়াকে গতি দিতাম, গতি ফিরাতাম, বাঁক ফিরাতাম। এখানে একটু বাধ দেওয়া, ওখানে খাল বানানো, নদী বানানো, পুকুর-কাটা-দিঘি বানানো- এই সব। কেউ বলত, ‘তোরটা ছোট খাল অইছে। আর আমারটা দেখ, কত বড়। নদীর লাহান’- এই সব।
জ্যৈষ্ঠের জল মাথায় করে নিয়ে যেত খর-বিচালি, শুকনো লতা-পাতা, কাঠের টুকরো, বাঁশের টুকরো, পাখির পালক। আর থাকত আমাদের শিশুদের হাতের কোমল স্পর্শ।
মা বলতেন, ‘নতুন পানি। নামিছ না। জ্বর অইব।’
কিন্তু যদি নতুন পানিতে না-যাই, অনেক শিশুর সঙ্গে পানিতে শোরগোল না তুলি, তা হলে মা-ই বলবেন, ‘কিরে, খেলতে যাস না কেন? জরজারি অইল নাকি?’
কপালে হাত রাখবেন। ‘কই, জ্বর অয়নাইত? বোহে ধরছে?’
এই বলে মা আর অপেক্ষা করতেন না। পিঠা কিংবা গুড়মুড়ি, চাল ভাজা কিংবা তিলের মোয়া এনে দিতেন। নাকে-মুখে খেয়ে চম্পট দিতাম আমি। মা আর পায় কোথায় আমাকে?
দক্ষিণের খালটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে পৌঁছোতাম এক দৌড়ে। নতুন পানির সঙ্গে এসেছে নতুন মাছ। পুঁটি মাছ- তার গায়ে রঙের রেখা, খলিশা মাছের পাখনায় কারুকাজ, টাকি আর শোল মাছ পোনা নিয়ে মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও আছে হেলিকপ্টারের মতো টেংড়া, সোনালি রঙের পাবদা, নিরীহ রয়না। সেখানে ঝাকি জাল, ধর্ম জাল, বেড় জাল দিয়ে মাছ ধরার হিরিক পড়েছে।
গফুর, সুরুজ, পানু, ছালমা বড়শিতে ভাত গেঁথে গেঁথে ধরছে পুঁটি মাছ, টেংরা মাছ, বেলে মাছ। আর নতুন পানি পাটখেত, ধানখেত আর মরিচ খেতের তল বেয়ে বেয়ে যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে, ঘাসের সঙ্গে, পাতার সঙ্গে, খড়বিচালির সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানে অন্য শিশুদের মাছ ধরার খেলা চলছে। আমি মিশে যেতাম মাছ ধরার সেই মহা উৎসবে। জ্যৈষ্ঠের জলের এই নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারতাম না আমরা কেউই।
ইতোমধ্যে আষাঢ় এসেছে। উপরে-নিচে জলের সমারোহ। বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি। অবিরত বৃষ্টির জল আর নদীর জলে টইটুম্বুর হয়ে উঠেছে পুকুর, খাল-বিল, ডোবা-নালা। জ্যৈষ্ঠের জলের মতো চঞ্চলতা নেই তার। হালকা চালে হামাগুড়ি দিয়ে চলার শিশুত্বও নেই। অনেক জলের অনেক স্রোত নিয়ে সে হয়ে উঠেছে জবরদস্ত।
উত্তরের পুকুর পাড়ে অসংখ্য গাছ। পাড় থেকে বেঁকে গিয়ে পুকুরের উপর দিয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে আমাদের সবার প্রিয় আমগাছটি। আমাদের সেই বিস্ময়কর শৈশবে দেখেছি, মানুষেরই শুধু নাম থাকত না। গোরু-ছাগল, গাছগাছালি, খাল-বিল-পুকুর- সবারই নাম থাকত। এই গাছটির নাম ছিল বেলে আমগাছ। ডাক নাম বাইল্লা আমগাছ। বর্ষার শুরুতেই বাবা বাইল্লা আমগাছের তলার পুকুরে ডুব দিয়ে দিয়ে দেখে নিতেন কোনো ডালপালা, বাঁশের কঞ্চি বা অন্য কোনো শক্ত বস্তু আছে কি না। আমাদের সবার অজান্তে তিনি পুকুরের তল পরিষ্কার করে রাখতেন। যে-কোনো সময় শুরু হয়ে যাবে বাইল্লা আমগাছের মগডাল থেকে পুকুরের জলে ড্রাইভ দেওয়ার প্রতিযোগিতা। শোনা যায়, একজন শিশু নাকি এই গাছ থেকে লাফ দিয়ে পুকুরে পড়ে আর উঠে আসেনি। অনেক খোঁজাখোঁজির পর দেখা গেছে, সে জলের তলে একটি বাঁশের কঞ্চিতে গেঁথে আছে। মৃত সেই শিশুটির পরিচয় আমরা জানতে পারিনি কখনই। অপয়া গাছটিকে কেটে ফেলার কথা বলেছিল কেউ কেউ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাটা হয়নি। আর কোন কালের সেই ট্র্যাজেডিও মুছে গেছে সবার স্মৃতি থেকে। শুধু বাবা আমাদের কল্যাণের কথা ভেবে গোসল করতে নামলেই একবার ঘুরে যান বাইল্লা আমগাছের তলার পুকুরপাড়টিতে।
বর্ষায় এই পুকুরটি টলটলে পানিতে টইটুম্বুরর। স্রোতের টানে কচুরিগুলো কোথায় চলে গেছে তার খোঁজ নেই। শীতকালের মতো বড় বড় কচুরিতে ভরপুর জবুথবু ছোট পুকুর নয় সে আর। এখন সে বিশাল। খাল থেকে যে নালাটি এই পুকরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বর্ষার পানিতে এখন আর তার অস্তিত্ব নেই। বাজারে যাওয়ার নৌকাগুলো, ঘাস কাটার নৌকাগুলো, নাইয়র যাওয়ার নৌকাগুলো এখন ভিড়ে এই পুকুরের উত্তর পাড়ে। আর দক্ষিণ পাড়ে গোসলের ঘাট। পশ্চিম পাড়ের বিশাল বাগানের বেলে আমগাছটি আমাদের দখলে। গাছটির ডালে ডালে পনেরো-বিশজন শিশু। একজনের পর একজন নয়- প্রায় একসঙ্গে চার-পাঁচজন ড্রাইভ দিচ্ছে পুকুরের জলে। তারপর তলা অবদি গিয়ে ভুস করে ভেসে উঠছে কে কোন দূরে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায়, দুপুর গড়িয়ে যায়, আমাদের উঠার লক্ষণ নেই। মা এসে ডেকে গেছেন। চাচি, জেঠি, বড় আপু, মেজো দাদি- যে যখনই পুকুর পাড়ে এসেছেন সে-ই উঠার জন্য আমাদের তাড়া দিয়ে গেছেন। কিন্তু কে পাত্তা দেয় কার কথা? এক সময় বাবা লাঠি নিয়ে আসবেন। তাড়া দেবেন। আমরা কেউ আর তখন গাছের ডালে নেই। পুকুরের পাড়েও নেই। সাঁতার কেটে সোজা চলে গেছি পুকুরের মাঝখানে। কখনো কখনো বাবা লাঠি নিয়ে এ পাড়ে আসেন তো আমরা ওপাড়ে চলে যাই। বাবা ওপাড়ে যান তো আমরা এপাড়ে চলে আসি। এক সময় বুঝতে পারি যে, অবস্থা সুবিধার নয়। তখন রক্তজবা চোখ নিয়ে এবং গা ভর্তি শেওলা আর ময়লা নিয়ে যখন আমরা উপরে উঠে আসি তখন এক একজনকে কালো পিচ্চি ভ‚তের মতো লাগত। এই আজব চেহারা-সুরত নিয়ে যখন মায়ের সামনে দণ্ডায়মান হতাম, তখন মা ভ‚ত দেখার মতই আৎকে উঠতেন। কিন্তু আবুলের মায়ের মতো ‘গোলামের পুত গোলাম’ বলে দৌড়ানি দিতেন না। বরং কান ধরে হিড়হিড় করে পুকুর পাড়ে নিয়ে সাবান মেখে গোসল করিয়ে দিতেন। বড় আপুকে বলতেন, ‘নে। এইডার শইলে তেল মাইখ্যা দে।’
বিকেল তিন-চারটার দিকে দুপুরের খাবার খেয়ে আবার চম্পট দিতাম। আমাদের উত্তরের পুকুরে আর তখন নয়- সানকিভাঙ্গা সাঁকোর পাড়ে তখন চলছে পাড়ার সব শিশুদের জলখেলা, মহা কোলাহল। এখানে বিষয়টি আর পাড়ার বা পারিবারিক নয়। কয়েক গ্রামের শিশুরা মিলে রীতিমতো একটি আন্তর্জাতিক উৎসব করে তুলেছে। সেই উৎসবমুখর পরিবেশে নিজের অজান্তেই কখন যে পানিতে নেমে পড়তাম, সত্যি খেয়াল থাকত না কিছুতেই। সাঁকো থেকে খালের জলে ঝাপিয়ে পড়ার সেই আনন্দে ছেদ পড়ত যখন পাশের বাড়ি থেকে ফুফি এসে ধরে ফেলতেন খপ্ করে। অনেক ছেলে-মেয়েদের এই স্নান-উৎসব থেকে তার নিজের ছেলেকে নয়, মেয়েকে নয়- আমাকে কেন যে পাকড়াও করতেন তা বুঝতে পারতাম না। শুধু জানতাম, ফুফির হাতে ধরা পড়লে যৎসামান্য আনন্দের ব্যাপার আছে। তিনি সোজা আমাকে নিয়ে যাবেন বাড়িতে। আর এটাসেটা হাতে দিয়ে বলবেন, ‘নে, খা। সুরুজেরে কইস না। ডুবাইতে ডুবাইতে পেটটারে তো খালি কইরা ফালাইছছ। পানির কাছে আর যাবি না। বুজলি? ভাইজু দেখলে আস্ত রাখব না- মাইরা ফালাইব একদম। যা। সোজা বাইত যা।’
সন্ধ্যার দিকে যখন খড়ের একটা পুটলি বা সিদ্ধ করা জামবুরায় লাথি দিতে দিতে বাড়ির দিকে আসতাম, তখন পিছন থেকে শক্ত করে আমার কান চেপে ধরত শাহজাহান ভাই। বলত ‘আইছ সোনার চান? যাও- বাইত যাও। সারা বাড়ি খুঁইজ্যা মা টং অইয়া আছে। পানিতে পানিতে ভাইস্যা বেড়ানো দেখাইব।’
ভয়ে ভয়ে মার কাছে গিয়ে যখন সুবোধ ছেলেটির মতো দাঁড়াতাম, মা তখন টায়ার লাগানো কাঠের খরম এনে দিয়ে বলতেন ‘পা ধুইয়া ঘরে যা। খবরদার, আধোয়া পায়ে বিছানায় উঠিস না।’
বুঝতাম, শাহজাহান গুল মেরেছে। মা আসলে আমাকে খুঁজেইনি।
শৈশবের দিনগুলোতে পানির সঙ্গে একটি গোপন বোঝাপড়া ছিল আমার। পানি আমাকে বুঝত। আমি পানিকে বুঝতাম। অন্ধকার রাতে বা জোছনা-রাতে জ্যৈষ্ঠের স্বচ্ছ জলে মাছ শিকার করতে যেতেন ছোট কাকু কিংবা বড় ভাই। সঙ্গে নিতেন আমাকে গফুর বা আবুল বা জাহাঙ্গীর যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করত। কাকু বলতেন, ‘হ তোরে লইয়া যাই? পাগল। তোর যাওয়ার কথা হুনলেই তো মাছ দৌড়াইয়া পালাইব।’
এদের কাউকেই নিতেন না কাকু বা ভাইজু। বলতেন, ‘মন্নান যাইব। ও বিলাইর মতো হাঁটতে পারে। মাছের বাবার সাধ্য নাই টের পায়। পানিই তো লড়ে না। টের পাইব কেমনে?
খালের বা পুকুরের পাড় ঘেষে কিংবা পাটখেত-ধানখেতের আলের স্বচ্ছ জলে শুয়ে থাকত শোল মাছ, বেলে মাছ, টাকি মাছ, শিং মাছ, মাগুর মাছ চিংড়ি মাছ। টর্চের আলোতে মাছগুলো পরিষ্কার দেখা যেত। কাকু টর্চ মেরে মেরে সন্তর্পণে হেঁটে যেতেন। পিছনে পিছনে ডুলা হাতে আমি হাঁটতাম নিঃশব্দে নীরবে। মাছ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কাকু পিছনে ইশারা দিতেন। আমি জাদুমন্ত্রে দাঁড়িয়ে যেতাম। কোচের ঘাই পড়ত মাছের পিঠে। ডুলায় মাছ রেখে আবার টর্চ মেরে শতর্কতার সঙ্গে এগুয়ে যেতে হবে। কথা হবে না। হাসি-কাশি-হাছি না। পানি বুঝবে না পানি মারিয়ে মাছ মারা হচ্ছে। মিন শিশুদের তুলে নেওয়া হচ্ছে তার বুক থেকে, পেট থেকে, পিঠ থেকে। পানিতে হেঁটে হেঁটে পায়ের আঙুলের চিপায় ঘা হয়ে যেত। কিন্তু এসব নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ডুলা যখন ভরে যেত এবং রাতও যখন গভীর হয়ে আসত তখন কাকু বলতেন, ‘চল যাইগা। বহুত অইছে।’
বাড়িতে ফিরে আঙুলের ফাঁকে কেরোসিন তেল দিয়ে ঘুমোতে যেতাম আর স্বপ্নে দেখতাম জলের তলে মাছের সঙ্গে বাস করছি। বিচিত্র রঙের অসংখ্য মাছ আর মাথার উপরে জলের আকাশ।
এক সময় দেখতাম খালে-বিলে ফুটে আছে অসংখ্য তারা। বিশেষ করে পাট কেটে খালি করে দেওয়া হয়েছে যেসব খেত- সেই সব খেতে ফুটে আছে শতসহস্র তারা। জলের উপরে ভেসে থাকা শাপলা ফুলগুলোকে দূর থেকে দেখলে তারা-ই মনে হয়। কখনো কখনো হার মানায় অন্ধকার রাতের দূর আকাশের তারাকেও। কাঁপছে একটু একটু। দুলছে ডাইনে-বাঁয়ে। মৃদু ঢেউ তুলছে শান্ত জলের উপর। আকাশও যেন নড়ছে। জলকে বলি, ‘ও জল, স্বচ্ছ টলটলে জল, তুমি এত সুন্দর কেন? কে যে বলে তোমার কোনো রং নেই- জানি না। আমি তো দেখি, তোমার শরীরে শুধু রঙের খেলা। আকাশে যত রং আছে সব রং তুমি মেখে নাও তোমার তরল শরীরে। ধানের রং, পাটের রং আর এই বিচিত্র রঙের শাপলার রঙে তুমি যে কত রঙিন হয়ে ওঠ তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে।”

আমি এই রঙের জগতে ঝাপ দিই। দেখি, বিচিত্র রঙের ঘাস, শেওলা, শালুক জলের তলে স্রোতের সঙ্গে দুলছে- ডাইনে-বায়ে, সামনে-পিছনে। যেন নৃত্য। ছন্দে ছন্দে দোল খাওয়া কিশোরীর দল। সেই নৃত্যে যোগ দিই আমি। স্বচ্ছ পানির তল দিয়ে যখন ডুব সাঁতার দিই তখন জলের ছন্দ আমাকেও পেয়ে বসে। বিচিত্র বাঁকমোড় নিয়ে ডুবসাঁতার দিয়ে আমি চলে যাই জলের আকাশে- তারাদের কাছে। শাপলা ফুল তুলে তুলে রাখি শালুক পাতার উপর। যেন আকাশের তারা কুড়ানোর খেলা।
মাইলগখানেক দূরে মেঘনা নদী। আমরা যারা খুব ছোট, আট-নয় বছর বয়স তাদের কাছে শুধুই স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্ন এক দিন বাস্তব হয়ে গেল। মাঝিবাড়ির সুরুজ, ছৈয়াল বাড়ির আক্কাস আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে গেল মেঘনার তীরে। বাড়ির কাছে এই বিপুল জলের জগৎ কেন এত দেরি করে দেখতে এলাম সেই দুঃখে বাঁচি না আমি। নদীতে কত বিচিত্র পাল তোলা নৌকা, মাছ ধরার নৌকা, মালামাল পরিবহনের নৌকা, গুনটানা নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ- এসবের ইয়ত্তা নেই। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর, মেঘনার জলের স্বভাব। এর রং, রেখা, রূপ, তাল, লয়, ছন্দ একেবারেই আলাদা।
আমি যখন মেঘনার এই বিপুল সৌন্দর্যে বিমোহিত তখন ফুফাতো ভাই সুরুজ নাকের হিঙ্গুল হাতে মুছতে মুছতে মহা পণ্ডিতের মতো বলছে, ‘জানস, এই গাঙ্গে, পানির নিচে গঙ্গীমা থাহে। হেয়ই গাঙ্গে ঢেউ তোলে, বন্যা লাগায়। কামডা কী এমন বড় বড় ঢেউ তুইল্যা ? বন্যা দেওনের কাম কী, ক?
আক্কাস আরও বড় পণ্ডিত। সবুজের কথায় সায় দিয়ে বলে, ‘ঠিক কইছছ। নদীর পাড় ভাইঙ্গা যায়। মাইনষের ক্ষতি হয়। হের এগুলি করার দরকার কী!’
নদীর এই জায়গাটা চড়া। সমুদ্র-সৈকতের মতো। পানিতে নেমে অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যায়। ঠাঁই মিলে। পায়ের নিচে বালি। লোদ-কাদা নেই কোথাও। বিশাল বিশাল ঢেউ আসে। আমরা ঢেউয়ের উপর ভাসিয়ে দিই নিজেদের। ভয় নেই কোনো। নিচের দিকে পা বাড়িয়ে দিলেই মিলে মাটির নাগাল। খাল-বিল আর পুকুরের পানি থেকে এই পানি একেবারেই আলাদা। অদ্ভুদ এর গতি, চঞ্চলতা। আর উদারতায় অপরিসীম। সবাইকে সে গ্রহণ করে। কিন্তু রাখে না যেন কাউকেই। কিংবা গ্রাহ্য করে না কিছুকে, কাউকে। আমরা তার শরীরে মৎস পোকাদের চেয়ে বেশি কিছু নই। দূরে শুশুক ভেসে ওঠে। মুখ থেকে কিছুটা পানি পিচকারীর মতো উপরে ছিটিয়ে দিয়ে তলিয়ে যায় লেজ দেখিয়ে।
আক্কাচ এই বিপুল নদীর তলদেশের সব খবর জানে। সেখানে নাকি আরেকটা দেশ আছে। ওখানে বসবাস করে দৈত্যদানা, হাঙ্গর, কুমির। শুনে আমি ভয় পেয়ে যাই। জটপট উঠে আসি তীরে। আক্কাস অভয় দেয়।‘আরে বুদ্দু! ওরা তো কম পানিত আইয়ে না। আয়, আয়- নাইম্মা আয়।’
মুষলধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে জল খেলার আনন্দ নিয়ে আমাদের শৈশব কেটেছে। বৃষ্টির জলের ধারা নানা দিকে প্রবাহিত করার খেলা নিয়ে আমরা মেতে থাকতাম, পুকুরের জলে কান পেতে বৃষ্টির শব্দ শুনতা। জলের কতটা নিচে বৃষ্টির শব্দ পৌছোয়, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে মতান্তর আর ঝগরা করতাম। ডুব দিয়ে যতই নিচের দিকে যেতাম পানির উপরে বৃষ্টি শব্দে ততই যেন গম্ভীর আর রহস্যময় হয়ে উঠত। আর এই ঐন্দ্রজালিক রহস্যময় শব্দ শোনার জন্য আমরা পুকুরতলে মাটির সঙ্গে মাছের মতো শুয়ে থাকতাম। একজন আরেজনের সঙ্গে আকারের ইঙ্গিতে কথা বলতাম। গভীর থেকে গভীরতর জলে গিয়ে ডুব দিয়ে মাটি তোলার খেলা খেলতাম। কলা গাছ আর কলা গাছের ভেলা ছিল আমাদের নিত্য সঙ্গী। শৈশবের জলের জীবনে এ ছিল আমাদের আশ্রয়।
অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছি। আজ আর সেসব খুঁজে পেতেও চাই না। শুধু খাল, বিল আর পুকুরের জলের উপর বৃষ্টি পড়ে যে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময়তা তৈরি করত, যে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি হতো, সেই সঞ্চয়টুকু আজও ধারণ করে আছি। এখনো তাই ভালোবাসি জীবনকে, জলের পৃথিবীকে।
চলবে